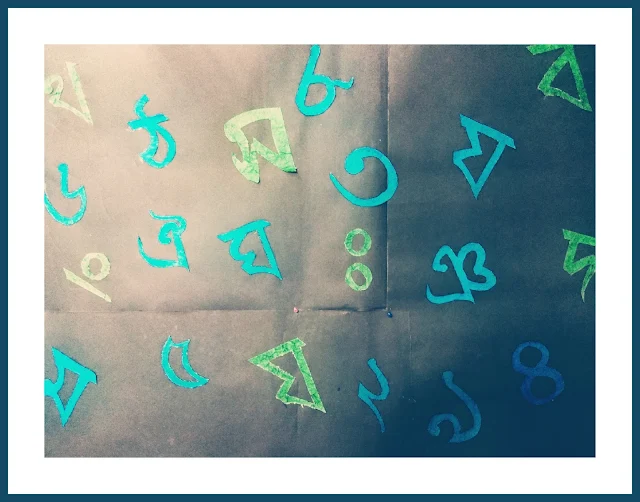প্রশ্ন ১) কবিতা লেখার শুরুর দিনগুলোর কথা একটু বলো
উত্তর— আক্ষরিক অর্থে কবিতা লেখা শুরুরও বেশ কয়েকবছর আগে, খেলাচ্ছলে কিছু প্রেমপত্র লিখতে গিয়ে আমি টের পাই, সেই কৃত্রিম লেখাগুলোর ভেতর দিয়েও, আমার যোগ্যতার অতিরিক্ত কিছু সৌন্দর্য ও সুষমা, আমার সম্পূর্ণ অবচেতনেই প্রকাশিত হয়ে পড়ছে। সেসব চিঠি যে শুধু নিজের জন্যই লিখতাম তা নয়, বরং বন্ধুবান্ধব অনেকের বকলমেই সেই পাপ আমি করেছি। করতে করতে এক বিপজ্জনক খেলায় নিজেও জড়িয়ে পড়েছি। ১৭/১৮ বছরের উন্মত্ত কৈশোরে জড়িয়ে পড়েছি ফিল্মি আবেগ নির্ভর মিথ্যে প্রেমের যন্ত্রণাদায়ক সম্পর্কে। কম বয়সের মোহে সেই সম্পর্কের রেশ টেনেছি বছর তিনেক। তারপর যথারীতি তা একদিন ফুরিয়ে যাবার সময় এসেছে। দু’জনের পথ, প্রাকৃতিকভাবেই পৃথক হয়ে পড়েছে একদিন। কিন্তু ফর্মুলাবদ্ধ সমাজের চোখে ঘোরতর অন্যায় হয়ে দাঁড়াল সেই বিচ্ছেদ। পাড়া প্রতিবেশী থেকে শুরু করে আমার আত্মীয় বন্ধু প্রায় সকলেই সেই বিচ্ছেদের জন্য আমার অপদার্থতা আর সামাজিক অযোগ্যতাকেই দায়ী করতে থাকল। আমি ভয়াবহভাবে একা হয়ে গেলাম। এমনকী আমার বাড়ির লোকেরাও সে সময় আমাকে করুণার চোখেই দেখতে শুরু করেছিল। তখন আমি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিষয়ে স্নাতকস্তরের ছাত্র। দিনের বেলা কলেজ সেরে, বাড়ি ফিরতাম বিকেলে। তারপর সন্ধে অব্দি বালিশে মুখ গুঁজে পড়ে থাকতাম, যতক্ষণ না অন্ধকার নেমে আসে চারপাশে। দিনের বেলা আলোয় বাড়ির বাইরে বেরতে আমার ইচ্ছেই করত না। আমিও কারুর মুখ দেখতে চাইতাম না, অন্য কেউ আমাকে দেখুক তাও চাইতাম না। সন্ধের আবছায়ায় বাড়ি থেকে বেরিয়ে হাঁটতে হাঁটতে প্রায় চল্লিশ মিনিটের পথ পেরিয়ে পৌঁছতাম পাটুলি সংলগ্ন বাইপাসের ধারে। তখন সবে নির্মিয়মান বাইপাসের ধারগুলোয় শুধু অন্তহীন মাছের ভেড়ি। ভেড়ির পর ভেড়ি। দুটো ভেড়ির মাঝ বরাবর চলে গেছে সরু সরু আলপথের মতো রাস্তা, মিশে গেছে দূরের ঘন অন্ধকারে। এখন যেখানে ‘বেণুবনছায়া’, সেখানে তখন নিশ্ছিদ্র কুয়াশাঘন অন্ধকার, জলায় জলায় জমাট বেঁধে থাকত। পুবদিকের অন্ধকার চিরে শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখার ট্রেন চলে যেত গড়িয়া স্টেশনের দিকে। তারপর সোনার থালার মতো চাঁদ উঠত রেললাইনের উত্তর-পূর্ব কোণ থেকে। আমি একা জলের ধারে বসে থাকতাম ঘন্টার পর ঘন্টা, সন্ধের পর সন্ধে। বসে বসে দেখতাম কালো জলের ওপর কেমন ঝাঁপিয়ে পড়েছে ঝকঝকে তারায় ভরা রাত্রির আকাশ। দূরে, আলপথের কুয়াশা ভেদ করে, চাদর জড়ানো দিনমজুরের দল বিড়ি টানতে টানতে চলে যাচ্ছে ক্রমাগত রেললাইনের দিকটায়… সেইসময় নিজের অজান্তেই আমি ধ্যানস্থ হয়ে পড়তাম যেন। সেই নির্জন, নৈসর্গিক অন্ধকারে, তারায় ভরা অন্তহীন আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে আমার একবিন্দু প্রাণ যেন এক মহাজাগতিক জীবনের ইশারা অনুভব করত। বেশ কিছুদিন এইরকম চলার পর বুঝলাম, অনেক অনেক কথা যেন জমা হচ্ছে আমার ভেতরে, কিন্তু সেইসমস্ত আকাশকুসুম ভাব প্রকাশের ভাষা যে আমি জানি না। বুকের ভেতর কী যে জমাট সেই অবস্থা, আজও বলে বোঝানো সম্ভব নয়। তাছাড়া সেইসব কথার ভাব এমনই, যে তা ভাষায় যদি প্রকাশ করাও যায়, শুনবেটা কে? এই বিশ্বচরাচরে আমার পরিচিত এমন কোনও মানুষের মুখ তখন মনে পড়ত না, যাকে গিয়ে আমার মনের কথা বলতে পারি। সেই কথা কিন্তু কোনও সম্পর্ক ভাঙার কাঁদুনিমাত্র নয় মোটেই। ফেলে আসা সম্পর্কের সঙ্গে তার কোনও সম্পর্ক প্রায় নেই বললেই চলে, বরং সেইসমস্ত কথা যেন আমার এই একলা হয়ে পড়ার অপেক্ষাতেই বুকের ভেতর নির্মমভাবে ঘাপটি মেরে ছিল এতকাল। ক্রমান্বয়ে সেই কথাগুলোই আমাকে চাপ দিতে থাকল লেখার। গর্ভস্থ শিশু যেমন প্রসবের জন্য মায়ের পেটে চাপ দেয়, সেইরকমই অনেকটা। একটা দুটো লেখার সূত্রপাত হয় তখনই। কিন্তু কবিতা লেখা তো দূর, সমসাময়িক কবিতা পড়ার দীক্ষাও তো তখন আমার ছিল না, ফলে কাঁচা ভাষায় অনিয়ন্ত্রিত আবেগের স্রোত বয়ে যেত সেসব লেখার ভেতর দিয়ে। তখন এক বন্ধু আমায় একদিন ‘জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা’ বইটা ওদের পারিবারিক সংগ্রহ থেকে দেখাল। ওর এক পিসিকে সেই বই উপহার দিয়েছিলেন স্বয়ং লাবণ্য দাশ। উপহারের পাতায় তার ‘নির্জন স্বাক্ষর’ দেখে খুবই শিহরিত হয়েছিলাম, মনে আছে। সেই আমার প্রথম, পাঠক্রমের বাইরে, জীবনানন্দ পড়ার শুরু। তার কিছুদিনের মধ্যেই ঈশ্বরের কৃপায়, আর দু’একজন বন্ধুর সাহয্যে হাতে এল ‘শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা’, বিনয় মজুমদারের ‘ফিরে এসো চাকা’, ‘উৎপল কুমার বসুর শ্রেষ্ঠ কবিতা’(কবিতা সংগ্রহেরও অনেক আগে বেরিয়েছিল)… এইসব। ফলে জীবনানন্দ পরবর্তী বাংলা কবিতা সম্পর্কে একটা প্রাথমিক ধারণা হলো আমার। তখন একদিন জানলাম, আমাদের পাড়ার বাপ্পা দা নাকি এই সময়কার (নয়ের দশকের) একজন উজ্জ্বল কবিতাপ্রয়াসী। পোশাকি নাম যার সন্দীপ চট্টোপাধ্যায়। গেলাম ওর কাছে। ও তখন একটা বিশাল উপকার করেছিল আমার। বলেছিল, হাজার বছরের বাংলা কবিতায় নিয়মনিষ্ঠ ছন্দের ভূমিকার কথা। উৎসাহ দিয়েছিল ছন্দ শেখার। সেটা ৯৫ সাল হবে। আমি ছন্দ শেখায় যত্নবান হলাম। সেসময় নয়ের দশকের এক ব্যতিক্রমী উজ্জ্বল তরূণ-কবি দীপঙ্কর বাগচীর সঙ্গে আমার আলাপ। ওর কাছেও ছন্দ এবং কবিতা বিষয়ক কিছু সাহায্য তখন পেয়েছি। এর পরের দু-তিন বছর, ছন্দ শিখতে শিখতে যাকিছু লিখেছি, তার কিছুই আর পরবর্তী সময় কোথাও রাখিনি, কারণ আমি কীভাবে যেন বুঝে ফেলেছিলাম-- কবিতার চেহারা আর কবিতা এক জিনিস নয়। সেটাই ছিল আমার কবিতা-জীবনের প্রথম এবং কঠিনতম পরীক্ষা। ছন্দে লিখব, কিন্তু ছন্দ লিখব না, লিখব বিশুদ্ধ কবিতা। সেই পরীক্ষা বা সাধনার প্রথম সিদ্ধাই আমার প্রথম কবিতার বই ‘ব্যক্তিগত আলেখ্যের প্রতি’। রচনাকাল ৯৮, ৯৯ । এই সময়কালেই আমি স্পষ্ট করে টের পাই, কবিতা আমি লিখি না, বরং আমাকে রচনা করে কবিতা স্বয়ং। বুকের ভেতর জমাট হয়ে থাকা কথাগুলো কেমন যেন আপনাআপনি ছন্দবদ্ধ হয়ে আমার কলমের ডগায় নেমে আসে প্ল্যানচেটের মতো। সেইসময়কার আদিতম রচনাটির অংশবিশেষ ছিল এইরকম—
‘কবিতার দোষে আমি কাপালিক হয়ে যেতে পারি। / যে দেহ শব্দের লাশে ব্যোম হয়ে ছুঁয়েছে স্তব্ধতা, / গোপন পাঁজরে আজ স্বীকার করেছি যার কথা, / আগুন যজ্ঞের নীচে পুড়ে যাওয়া সে দেহ আমারই...
...কবিতার দোষে আমি কাপালিক হয়ে যেতে পারি / অর্থাৎ কবিতা লিখে কবি হতে পারিনা কক্ষনো...
যা কিছু রচনা নয়, ততটাই লিখে রাখা চলে; / যেমন আড়াল গেঁথে, হয়তো কেউ তাকে স্পর্ধা বলে।’
এই লেখাটির সূত্র ধরেই একদিন নয়ের দশকের অন্যতম প্রধান কবি অনির্বাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমার আলাপ এবং সেই সূত্রেই কলেজস্ট্রিট কফিহাউসের ‘গান্ধার’ পত্রিকাগোষ্ঠীর বন্ধুদের সঙ্গে মেলামেশার সূত্রপাত। অনেকটা এইরকমই আমার কবিতা লেখা শুরুর দিনগুলো।
প্রশ্ন ২) তুমি তো উচ্চাঙ্গসঙ্গীত পছন্দ করো, এই অভ্যেসটা কী করে হলো?
উত্তর-- সুরের প্রতি অনুরাগ আমি পেয়েছি মামাবাড়ির সূত্রে। মা-মাসিদের গানের গলা ছিল বড্ড সুরেলা। যে-সমস্ত গায়ক গায়িকার গলায় ধ্রুপদী দক্ষতা বেশি, তাঁদের বিশেষ ভক্ত ছিল আমার মা-মামা-মাসিরা সবাই। তাছাড়া আমার বাড়ির ঠিক উল্টোদিকের বাড়িতেই ছিল একটা গানের স্কুল। সারা বিকেল-সন্ধে জুড়ে নানান রাগরাগিণীর তালিম চলত। আমি যে খুব মন দিয়ে শুনতাম তা নয়, কিন্তু পরবর্তী সময় দেখেছি সেইসব সুর আমার অবচেতনে কেমন অলৌকিকভাবেই সঞ্চিত হয়ে থেকে গিয়েছিল। ওই যে একলা দিনগুলোর কথা বলছিলাম, সেই সময়ই একদিন ঘুরতে ঘুরতে আমি ঢুকে পড়েছিলাম ‘দক্ষিণী সঙ্গীত সম্মেলন’-এর বার্ষিক আসরে। টালিগঞ্জে, আমার বাড়ির কাছে, সেই আসর এখনো বসে প্রতি জানুয়ারির ৮/১০ তারিখ নাগাদ। প্রায় চল্লিশ বছর ধরে বসছে। সেই যে একবার ঢুকে পড়লাম, তারপর থেকে গত বাইশ-তেইশ বছর যাবত আমি ঘোরতর আসক্ত হয়ে আছি ভারতীয় সঙ্গীতের অলৌকিক সৌন্দর্যময় ঐশ্বর্যে। কিছু কিছু রাগরাগিণী, উপযুক্ত পরিবেশনায় শুনে মনে হয়েছে এই সুর তো আমার বহুকালের চেনা। সেই চেনার বয়সকাল যেন বা আমার তৎকালীন বয়সের তুলনায় অনেকগুন বেশি। যেন কয়েক জন্মান্তরের ব্যবধান। উস্তাদ ফৈয়াজ খাঁ সাহেবের গাওয়া দেশ রাগ শুনে, বিদুষী মালিনী রাজুরকারের জৌনপুরি শুনে, বিদুষী কিশোরী আমনকারের বাগেশ্রী শুনে এই অনুভূতি আমার বারবার হয়েছে। এসব নিয়ে বেশ কিছু কবিতাও আমি বিভিন্ন সময় লিখেছি। জন্মান্তরের আখ্যানগুলো, বৃহত্তর অর্থে সঙ্গীত শোনার আগে পর্যন্ত আমার কাছে গল্প বলেই মনে হতো, এমনকী জাতকের কাহিনীও। কিন্তু ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত আমাকে জন্মান্তরের স্পষ্ট আভাস দিয়েছে। আমি জীবনে প্রথম বেনারস যাবার অন্তত ১৫/২০ বছর আগে থেকেই গভীরভাবে অনুভব করেছি যে বেনারসের সঙ্গে আমার জন্মান্তরের কোনও না কোনও যোগাযোগ আছে। সেই টান ব্যাখ্যাতীত। আমার ‘যে আরতি মণিকর্ণিকার’ বইটিতে সেই বিস্ময় আংশিকভাবে লিপিবদ্ধ।
বছর কুড়ি আগে যখন ডোভার লেন সহ অন্যান্য মিউজিক কনফারেন্স শোনা শুরু করি, টিকিট কাটারও পয়সা থাকত না। এর-তার থেকে টিকিট বা পাস জোগাড় করে কোনোক্রমে ঢুকতাম। সারারাত খিদের জ্বালায় ছটফট করতে করতেও গোগ্রাসে গানবাজনা শুনতাম, কিন্তু কিছু কিনে যে খাব, তার উপায় কোথায়? পকেট যে গড়ের মাঠ। আমার গানবাজনা শোনার দীর্ঘদিনের সঙ্গী স্বর্ণেন্দু সরকার তেমনই অনেক অসহায় এবং আনন্দঘন রাত্তিরে আমার প্রাণ বাঁচিয়েছে খাইয়েদাইয়ে। তবু সঙ্গীতের ওপর আমার আসক্তি দিন-কে-দিন বেড়েছে বৈ কমেনি। জন্ম থেকেই আমার গলায় সুর ছিল পর্যাপ্ত, মায়ের তাই ইচ্ছে ছিল গান শেখানোর, কিন্তু বাবার একার রোজগারে আর সেটা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। তবুও যত দিন গেছে, আমি সঙ্গীতের প্রেমে হাবুডুবু খেয়েছি ততই। আজ অনুভব করি, আমার লেখার পেছনেও সেই সঙ্গীত-প্রেমের ভূমিকা অপরিসীম। শব্দ বা বাক্যে প্রাণসঞ্চার করার ক্ষেত্রে সুরের ভূমিকা খুবই অলৌকিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। তাছাড়া সঙ্গীত-প্রীতির হাত ধরেই আমি ক্রমশ আচ্ছন্ন হয়েছি অধ্যাত্মবাদে। অনুভব করেছি, সঙ্গীত, ঈশ্বরের সঙ্গে কথোপকথনের শ্রেষ্ঠ এবং সূক্ষ্মতম পথ। আমরা তো গৃহী মানুষ, খাঁটি সাধু বা সাধক দেখার সুযোগ আমাদের খুবই কম, কিন্তু সঙ্গীতই আমার জীবনে সেই পরিসর, যা আমাকে শিখিয়েছে সাধক চিনতে। সাধনা বস্তুটিও ঠিক কী জিনিস আমি বুঝতে শিখেছি সেইসব সাধক শিল্পীদের দেখেই। আরো একটা ব্যাপার, আমাদের সমাজে যে সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়ানো রয়েছে বহুকাল যাবত, যা অবচেতনে বেশিরভাগ মানুষকেই আচ্ছন্ন করে রেখেছে, তার হাত থেকেও আমি চিরতরে মুক্তি পেয়েছি উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতেরই কৃপায়। বাবা আলাউদ্দিন খাঁ, পণ্ডিত ভাস্কর বুয়া বাখলে, উস্তাদ আব্দুল করিম খাঁ, উস্তাদ বিসমিল্লা খাঁর জীবনকথা, আমাকে এই অভিশপ্ত সাম্প্রদায়িক সমাজ থেকে বহুদূরের এক জন্নতে পাকাপাকিভাবে অধিষ্ঠিত করেছে, সম্ভবত বাকি সারা জীবনের জন্য।
এখন আমার মেয়ে সেতার শিখছে, আমি চাই ওর জীবনে, ওর সমগ্র জীবনব্যাপী, সঙ্গীত যেন প্রত্যক্ষভাবে ক্রিয়াশীল হয়, ক্রিয়াশীল থাকে। তাহলে আমার সঙ্গীত-প্রেম আরোই অর্থবহ হয়ে উঠবে আশা করি। আমি তো ঈশ্বর বিশ্বাসী, তাই মাঝে মাঝে ভাবি, হয়তো আমার মেয়ে একদিন প্রত্যক্ষ সঙ্গীতচর্চা করবে বলেই পরম রহস্যময়, করুণাময় ঈশ্বর আমাকে এত বছর ধরে পাক খাইয়েছেন এত অজস্র আসরে, মজলিশে।
প্রশ্ন ৩) গানের কথা আর কবিতার কথার মধ্যে ফারাক করবে? করলে সেটা কী?
উত্তর— গানের কথা অনেক ক্ষেত্রে কাব্য হয়ে উঠতেই পারে, যেমন কবীর-লালন-রবীন্দ্রনাথ কিংবা কবীর সুমনের বহু গান, কিন্তু তা সত্বেও গানের কথা আর কবিতার কথা সমার্থক নয় কিছুতেই। মনে রাখতে হবে, যে-গানকে সূক্ষ্মতম শিল্পের মর্যাদা দেওয়া হয়ে থাকে, তা মূলত সুরপ্রধান। কথা সম্বলিত গান সেই জায়গা কোনোদিনই দাবী করতে পারে না। সেটা একটা মিথোজীবী শিল্প। একে অন্যের ওপর নির্ভরশীল। কথা লিখতে গেলে সুরের কথা, সুর করতে গেলে কথার কথা মাথায় না রেখে উপায় থাকে না। কিন্তু কবিতা তার তুলনায় অনেক স্বাধীন। ছন্দের ছাঁচও যে কবিকে মানতেই হবে, তেমনও কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। সারাজীবন ছন্দে না লিখেও কেউ ওয়াল্ট হুইটম্যানের মতো চিরস্মরণীয় কবি হতেই পারেন। এমনকী গীতি-কবিতার ক্ষেত্রেও যে গীতলতা, সেও কিন্তু সুরের ভরসায় থাকে না। আবার দ্যাখো, গানের কথায় কখনোই ভারী শব্দের ব্যবহার বা ভাবের অতিরিক্ত বিমূর্ততা কাম্য নয়, সেক্ষেত্রেও কবিতার পক্ষে অনেকটাই স্বাধীনচেতা, স্বেচ্ছাচারী হওয়া সম্ভব।
প্রশ্ন ৪) তোমার কবিতা ভাবনায় একটা ধ্রুপদী চিন্তন লক্ষ করা যায়। এই ব্যাপারটা এল কীভাবে? মানে নয়ের দশকে যখন সশব্দ হাততালির কবিতা বাহবা পাচ্ছে, তখন তুমি সেদিকে না গিয়ে থাকলে কী করে?
উত্তর-- কবিতা লেখার অন্যতম শর্ত হিসেবে একজন কবিকে প্রথমে একজন শ্রেষ্ঠ কবিতা-পাঠক হয়ে উঠতে হয়। এই কবিতা পাঠের মধ্যে দিয়েই গড়ে ওঠে তার ব্যক্তিগত কাব্য সংস্কার। আমি যখন বাংলা কবিতা বা বিশ্ব-কবিতার পাঠ নিতে শুরু করেছি, তখন থেকেই লক্ষ করতাম, যাঁদের যাঁদের কবিতা আমার ভালো লাগে তাঁদের মধ্যে একটা গভীর সাদৃশ্য আছে কোথাও যেন। সেই সাদৃশ্যটি হলো ওই Sense of eternity বা শাশ্বতের ধারণা। হয়তো সেসব বিভিন্ন কবির বাহ্যিক জীবনযাপন, এমনকী কবিতার ভাষা একেবারেই আলাদা। কেউ ধরো খুব শান্ত, স্থিতধী, যেমন রবীন্দ্রনাথ বা রিলকে… আবার কেউ বেদম উন্মত্ত, উড়নচণ্ডী, যেমন বোদলেয়ার বা মধুসূদন… কিন্তু এই সমস্ত কবিকেই যে একই সঙ্গে আমার প্রাণে ধরল, তার প্রধান কারণ ওই মহাজাগতিক চিরন্তনতার বোধ, যা থেকে প্রকাশ পায় বিশ্বমানবতার আবহমান চেতনা। তার পাশাপাশি লক্ষ করে দেখলাম, যে আমার প্রিয় কবিদের সকলেরই কবিতায় আছে আশ্চর্য মন্ত্রশক্তি। খুব সম্ভব ওই চিরন্তনতার বোধের সঙ্গে এই মন্ত্রশক্তির একটা ব্যাখ্যাতীত সম্পর্ক আছে। মধুসূদন-রবীন্দ্রনাথ থেকে জীবনানন্দ-সুধীন্দ্রনাথ, রুমি-হাফিজ থেকে জিব্রান-গালিব কিংবা কীট্স্-ব্লেক থেকে ইয়েট্স্-ফ্রস্ট সকলের মধ্যেই ওই দু’টি জিনিসের আশ্চর্য সম্মেলন আমি লক্ষ করেছি অতি যত্নসহকারে। আর সেখান থেকেই আমার মধ্যে ‘ধ্রুপদী চিন্তন’-এর সূত্রপাত হয়তোবা। তারই দাবী অনুযায়ী আমি কবিতা লেখার প্রায় শুরু থেকেই ধ্রুপদী আঙ্গিকের চর্চাও সযত্নেই করেছি। আমার সামান্য সংখ্যক পাঠকমাত্রেই জানেন যে আমি সনেট বা চতুর্দশপদী কবিতায় সবিশেষ অনুরক্ত। তবে প্রিয় কবিতা বাছার ক্ষেত্রে আমি ধ্রুপদী আঙ্গিকের চেয়ে ধ্রুপদী ভাবনাকেই বেশি প্রাধান্য দিই, যার জন্য ওয়াল্ট হুইটম্যানও আমার প্রিয় কবিদের অন্যতম। ঠিক যেমন করে হিমেনেথের ‘Platero and I’ আমার অন্যতম প্রিয় কবিতার বই।
যেহেতু আমি কবিতার ব্যাপারে ভয়ানক সংস্কারাচ্ছন্ন, নাকউঁচু, তাই আমার সমসময়ের অধিকাংশ কবি এবং কবিতাকে আমি করুণাই করে এসেছি চিরকাল। যতই তারা হাততালি পান, যতই তারা বগল বাজান মিডিয়ায়, আমি ফিরে দেখারও প্রয়োজন বোধ করিনি। আমার খুব সৌভাগ্য যে অল্প হলেও আমার সমসময়ে আমি এমন কয়েকজন কবিবন্ধুকে পেয়েছি যারা কবিতার ব্যাপারে আমার মতোই বা আমার চেয়েও বেশি সংস্কারাচ্ছন্ন, আমার মতোই, তারাও ধ্রুপদী চিন্তনে ধারাবাহিক আস্থা রেখে আসছে। সেই সূত্রেই হয়তো কাছাকাছি আসার সুযোগ হয়েছিল আমাদের, যার ফলে পারস্পরিক ভাব বিনিময়ের মাধ্যমে লাভ হয়েছে হয়তো সবারই।
প্রশ্ন ৫) তোমার দশকের কবিতা নিয়ে তোমার মতামত কী?
উত্তর— অন্যান্য দশকের মতোই, নয়ের দশকের কবিতাকেও আমি স্পষ্ট দুটো ধারায় ভাগ করতে পারি। একদল গোড়া থেকেই দাদা-ধরা, প্রতিষ্ঠানমুখী, যশলোলুপ। নাচন-কোঁদন যা কিছু করেই হোক না কেন, নাম তাদের করতেই হবে। তাই তারা প্রথম থেকেই খাঁটি কবিতার ধারেকাছে ঘেঁষেনি কোনও দিন। বরং কবিতার শরীর ধার নিয়ে তারা লিখেছে সমসাময়িক বাজার অনুমোদিত চলতি-বিষয় এবং চালু-ভাষা অবলম্বনে বিচিত্র কিছু ছড়া। যেহেতু যোগ্যতার পরিবর্তে তাদের যোগাযোগ দক্ষতাই ছিল প্রধান সম্বল, তাই তেলখোর দাদাবাবুদের কাছে তাদের গ্রহণযোগ্যতাই ছিল বেশি। সময় মতো তারা তার স্বীকৃতিও পেয়েছে। নয়ের দশকের প্রধান কবি হিসেবে তাদেরকেই চিনেছেন সাধারণ অভাগা মানুষ।
অথচ এই নয়ের দশকেই লেখা হয়েছে এমন কিছু কবিতার বই, যার যথাযোগ্য সংকলন হলে জীবনানন্দ পরবর্তী বাংলা কবিতার ধারণা অনেকটাই বদলে যেতে পারে। যেসমস্ত কবিতার বই, তুমি চাইলে, পৃথিবীর যে কোনও সেরা কবিতার বইয়ের পাশাপাশি রেখেও পড়তে পারো। সেইসমস্ত অনামজাদা কবি, নিজেদের মনের আনন্দে মগ্ন হয়েই কবিতা লিখে চলেছে এখনও। ক্ষমতাবান দাদা-বাবুরা তাদের নানান লোভ দেখিয়েও বশে আনতে পারেননি। অথচ সেই বাবুসমাজ প্রবলভাবে চেয়েছিলেন, নিজেদের সাম্রাজ্য দীর্ঘস্থায়ী করার খাতিরে এইসমস্ত শক্তিশালী পথের কাঁটা যেনতেন ভাবে সরিয়ে ফেলতে। তার জন্য তাঁদের উদ্যোগের কোনও অভাবও ছিল না। তারপরেও তাঁরা বিশেষ পাত্তা তো পানইনি বরং উপেক্ষিতই হয়েছেন বারবার। তাই তাঁরা তাঁদের ছেড়ে যাওয়া সিংহাসনে এমন কিছু বন্ধ্যা ছড়াকারকেই বসিয়েছেন, যারা হাজার বছর রাজা হয়ে বসে থাকলেও পূর্ববর্তী সম্রাটের প্রভাব লঘু হবে না একফোঁটাও।
কিন্তু আমি বলি কী, এইসব ছকবাজি তো আজকের নতুন ব্যাপার নয়, তারপরেও জীবনানন্দ দাশ, বিনয় মজুমদার, শম্ভুনাথ চট্টোপাধ্যায়, তুষার রায়, পার্থপ্রতিম কাঞ্জিলালদের কোনোভাবেই আটকে দেওয়া গেছে কি? নয়ের দশকের অনালোচিত কবিদের মধ্যে অন্তত এমন তিনজন এখনও লেখার ভেতর আছে, যারা নিজেদের সমকালীন কাব্য-ইতিহাস নতুন করে লিখতে বাধ্য করবে একদিন। কারণ আমি যাদের কথা বলছি, তাদের লেখায় রয়েছে সেই অতিদুর্লভ Sense of eternity, যা খাঁটি কবিকে, মৃত্যুর ২০০ বছর পরেও আবার নতুন করে বাঁচিয়ে তুলতে পারে। উল্টোদিকে, সমসাময়িক উত্তেজনাপ্রসূত কবিতা, সময়ের সঙ্গে সঙ্গেই ফিকে হয়ে আসে আপনাআপনি।
প্রশ্ন ৬) পরবর্তী কবিদের লেখাকে কী চোখে দেখছ?
উত্তর— নয়ের দশকের কবিতা সম্পর্কে যা বললাম, তা শুধু নয়ের দশকেরই গল্প তো নয়, সাতের দশকেও এই একই গল্প ছিল, যা আজ সময়ের ব্যবধানে খুবই প্রকটভাবে পরিস্ফুট। কিন্তু নয়ের দশকে এসে সেই গল্পের প্যাটার্ন বদলেছে। আবার এই শতাব্দীর কবিদের মধ্যেও সেই একই ট্রেন্ড আমি লক্ষ করছি। একদল নির্লজ্জভাবে তেল দিচ্ছে প্রকাশ্যে, আবার একদল এসব থেকে সচেতনভাবেই দূরত্ব বজায় রেখে নিজেদের কবিতায় সাধনার পরিসরকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করে যাচ্ছে। নয়ের দশকের তুলনায় এই গল্পের প্যাটার্নও আবার বদলে গেছে অনেকটা। বিশেষত সোশ্যাল মিডিয়ার প্রভাবে আজকের এই প্যাটার্ন চেঞ্জ বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। যেমন তাৎপর্যপূর্ণ ছিল নয়ের দশকে কম্পিউটার এবং গ্লোবালাইজেশনের আবির্ভাব। কিন্তু যদি তুমি শাশ্বতের ধারণা থেকে বিষয়টা দ্যাখো, তাহলে দেখবে, খণ্ডচিত্রগুলোর বৈষম্য থাকা সত্ত্বেও আসলে মূল বিষয়টা থেকে গেছে একই। যোগ্যতার তুলনায় যোগাযোগ দক্ষতার কদর যে কোনও যুগেই বেশি। অথচ কবিতার ক্ষতিবৃদ্ধি হয়নি তাতে বিশেষ। ক্ষতি হয়েছে পাঠকের, পাঠরুচির। পাঠক নিজের সমকাল থেকে ক্রমশই পিছিয়ে পড়েছে এবং পড়ছে। সমকালীন শ্রেষ্ঠ কবির খোঁজ পাওয়ার আগেই ফুরিয়ে যাচ্ছে তার আহ্লাদের আয়ুষ্কাল।
প্রশ্ন ৭) সমসাময়িক রাজনীতি নিয়ে তোমার ভাবনার জায়গাটা ঠিক কী?
উত্তর— আমার এযাবৎ কথাবার্তা থেকে এটা নিশ্চয়ই বোঝা যাচ্ছে যে ‘সমকাল’ বিষয়টা আমার কাছে ‘চিরকাল’-কে চেনারই একটা উপকরণমাত্র। সমকালীন ভারতবর্ষ তথা বিশ্ব জুড়েই যে উগ্র সাম্প্রদায়িক রাজনীতির প্রকাশ দেখা যাচ্ছে, যুদ্ধের রাজনীতির প্রকাশ দেখা যাচ্ছে, নাক্ষত্রিক উচ্চতা থেকে দেখলে মনে হয় পৃথিবীতে এসব কোনও নতুন ঘটনাই নয়। এর মধ্যেও যা শাশ্বত, তা হচ্ছে একশ্রেণির শোষণ আর এক শ্রেণির শোষিত হওয়ার ইতিহাস, যার পুনরাবৃত্তি ঘটছে শতাব্দীর পর শতাব্দী, সভ্যতার পর সভ্যতাব্যাপী। সেই নিয়মেই মার খেতে খেতে আজও জেগে উঠছে দলিত সম্প্রদায়, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, আদিবাসী সম্প্রদায়... ধারাবাহিক আত্মহত্যার বিষাদ কাটিয়ে দীর্ঘতম মিছিল থেকে ডাক পাঠাচ্ছে কৃষকসমাজ... সমকালীন রাজনীতি আমাকে এমনই কিছু চিরকালীন বার্তা দিয়ে যায়, যা দলগত রাজনীতির ধারণা থেকে বহু দূরের ব্যাপার। সম্ভবত অন্য পৃথিবীর।
প্রশ্ন ৮) বিশ্ব-পরিস্থিতি, মানে প্যালেস্তাইন, গাজা, এসব তোমার লেখাকে প্রভাবিত করে?
উত্তর— এই প্রশ্নের উত্তরে একটা কবিতাই বরং উদ্ধৃত করতে চাই, তা থেকেই যা বোঝার বোঝা যাবে আমার ধারণা—
আতঙ্কবাদীকে লেখা চিঠি
আসুন আতঙ্কবাদী, পৃথিবীর ক্ষীণ শেষবেলায়
সিরিয়া ভারত ফ্রান্স বাংলাদেশ কিংবা কেনিয়ার
যেকোনও সূর্যাস্ত-প্রান্তে দু’মিনিট একটু বসা যাক;
লুটিয়ে ঘাসের গায়ে আগ্নেয়াস্ত্র, নিশ্চিন্তে বসুন।
দিনের ওপারে যায় দেখুন কীভাবে দিনমণি;
কীভাবে সমস্ত তেজ ত্যাগ-মন্ত্রে করে সম্বরণ;
কেননা তাকেও সরে যেতে হয়, রাতের হাতেই
সন্তানের, সভ্যতার, প্রতিপালনের ভার দিয়ে।
তিনি কি পারেন না নিজ-তেজে হতে আত্মঘাতী ছাই?
তিনি কি পারেন না রাগে অন্ধ হয়ে চির অন্ধকার
করে দিতে এ জগত? বিশেষত এই আমাদের
লোভ হিংসা ব্যাভিচারে রক্তারক্তি সংসার যখন...
তা তো তিনি করেন না কখনও; সে কি তেজের অভাব?
বরং সৃষ্টির ধর্ম এই তার, প্রেমধর্ম, স্নেহধর্ম এই...
তেজের মহিমা শুধু সম্বরণে হয় ফলপ্রদ;
ফলস্বরূপ সেই শিশু, আপনারও কি তেজঃবীর্যে নেই?
প্রশ্ন ৯) সাম্প্রতিককালে শঙ্খবাবু আর সুমনকে নিয়ে তোমার করা মন্তব্যে প্রচুর বাদ-বিবাদ হয়। এই দুই ব্যক্তিত্ব এবং তাদের কাজ বিষয়ে তোমার মতামত ঠিক কী?
উত্তর— শঙ্খ ঘোষ, একজন পণ্ডিত, প্রাবন্ধিক, সংবেদনশীল নাগরিক হিসেবে আমার কাছে বরাবরই শ্রদ্ধেয়। ওঁর বিষয়ে শুধু দুটো কথা বুঝতে আমার অসুবিধে হয়। প্রথমটি হল— শঙ্খ ঘোষের কবিতা। ‘দিনগুলি রাতগুলি’ বইটিতে আমি একজন সংবেদনশীল প্রেমিকের দেখা পাই, বৃহদর্থে ব্যথা পাই আনন্দ পাই তার ছোঁয়ায়। কিন্তু তার পর থেকেই আমি শঙ্খ ঘোষের কবিতায় পেতে শুরু করি সামাজ-শিক্ষার দায়িত্বপ্রাপ্ত একজন আচার্যকে। যিনি প্রচার করে চলেন নানান সামাজিক বার্তাসকল। সমসময়ের কাছে সাময়িক গুরুত্ব পাওয়া ছাড়া বৃহত্তর কাব্য-ইতিহাসে যাদের বিশেষ কোনও ভূমিকা নেই বলেই আমার মনে হয়। ‘মূর্খ বড়ো, সামাজিক নয়’ যিনি লেখেন তিনি যদি এমন সমাজসর্বস্ব হন, তাহলে তো লোকে ওঁর সম্পর্কে আলবাত বলবে-- সামাজিক বড়ো, মূর্খ নন মোটেই। হ্যাঁ, কবিতায় মূর্খের বিস্ময়, শিশুর বিস্ময় অবশ্যম্ভাবী শর্ত বৈ কী। একমাত্র ত্রিকালদর্শী স্থিতপ্রজ্ঞ লেখক ছাড়া, কাউকেই কবিতায় অত দায়িত্ববান দাদাবাবু হলে চলে না। দ্বিতীয়টি হলো— একজন মানুষ, যাঁর জীবনে অধ্যাত্মবাদের বিন্দুমাত্র জায়গা নেই, উপরন্তু, অধ্যাত্মবাদ প্রসঙ্গে যাঁকে নানারকম তুচ্ছতাচ্ছিল্য করতেও আমি প্রত্যক্ষ করেছি স্বয়ং, তিনি সারাজীবন ধরে রবীন্দ্রনাথকে ঠিক কী চোখে দেখলেন, সেটাই আমি ভেবে পাই না। অথবা রবীন্দ্রবিশেষজ্ঞই বা হয়ে উঠলেন কোন ম্যাজিক, কোন মন্ত্রবলে? কেননা রবীন্দ্রনাথের জীবনে প্রেম প্রকৃতি সমাজ, সবের ভেতর দিয়েই স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হচ্ছে অধ্যাত্মবাদ। অধ্যাত্মবাদের অর্থ যে পূজা-অর্চনা-ব্রত-রোজা-নমাজেই সীমাবদ্ধ তা তো নয়, ‘আকাশ ভরা সূর্য তারা’ গানটাতেও একটা গভীর আধ্যাত্মিক বিস্ময় আছে। এসব আড়াল করার চেষ্টা করে রবীন্দ্রনাথকে আদৌ বোঝা যায় কি? অথচ শঙ্খবাবু যেন সারাজীবন সেই ব্যর্থ চেষ্টাই চালিয়ে গেলেন। কিন্তু ওঁর ‘নিঃশব্দের তর্জনী’, ‘শব্দ আর সত্য’ ‘নির্মাণ আর সৃষ্টি’ জাতীয় প্রবন্ধের বই কিংবা ধরো, ‘সকালবেলার আলো’, ‘সুপুরিবনের সারি’ জাতীয় গদ্যরচনা আমার বিশেষ প্রিয়। এমনকী প্রাবন্ধিক হিসেবে ওঁর অভিভাবকত্বও আমার কাছে খুবই প্রার্থনীয়। ‘অন্ধের স্পর্শের মতো’ বইটি আমার সারাজীবনের পাঠক্রমে চির অমলিন হয়ে থাকবে, এ আমার স্থির বিশ্বাস।
কবীর সুমন আমার কাছে একটা ট্র্যাজেডি। আমি সুমনের আবির্ভাব থেকেই ওঁর গানের পরম ভক্ত। ওঁর লিরিক তুলনাহীন, ওঁর বিচিত্রগামী সুরের ধারণাও আমাকে বেশ অবাক করত। ওয়েস্টার্ন ক্লাসিক্যাল থেকে ভারতীয় মার্গ সঙ্গীত, সবরকম সুরেই ওঁর গানের গতিবিধি দেখে মুগ্ধ হতাম খুবই। কিন্তু লোকটা নিজের সীমা জানেন না। জানেন না, উনি ছাড়াও নানান মানুষ এখনও এই বাংলায় জীবিত আছেন যাঁরা নিয়মিত উঁচু দরের গানবাজনার খবর রাখেন। ওঁকে, শিল্পী হিসেবে আমি তবু হয়তো শ্রদ্ধা করতে পারতাম, যদি উনি এই বুড়োবয়সে বাংলা খেয়ালের নাম করে নিজের দুর্বিনীত অযোগ্যতার বদ-ঢেঁকুরটি না তুলতেন। উনি এত জানেন, আর এটা জানেন না যে ধ্রুপদী সংগীত মঞ্চে উঠে গাইতে গেলে গুরুকৃপা চাই, দীর্ঘদিনের সাধনামগ্ন তালিম চাই। ওঁর তো এসব কিছুই নেই। গলা থেকে সুরও বিদায় নিয়েছে বহু আগেই। তারপরেও যদি কোনও যশলোলুপ বামন চাঁদে হাত দিতে চায়, তার সম্পর্কে আর কীইবা বলার থাকতে পারে?
আর ব্যক্তিমানুষ হিসেবে কিংবা রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে সুমন সবদিক থেকেই অতি নিকৃষ্ট, অতি ধান্দাবাজ। তাই ব্যক্তি সুমন সম্পর্কে আমার কিছুই বলার ছিল না কোনও দিন, আজও নেই।
১০) তোমার এবং তোমার বন্ধুবৃত্তের কবিদের নিয়ে একধরণের কথা বাংলা কবিতা-বাজারে প্রচলিত।সেটা হল যে,তোমরা জীবনানন্দ, বিনয়ের অনুসারী এবং যখন তোমরা এক বিশ্বাস থেকে অন্য বিশ্বাসে যাও তখন একই সঙ্গে একই দিকে চলো। এই অভিযোগ সম্বন্ধে কি বলবে?
উত্তর— অভিযোগটি আংশিক সত্য বৈ কী। তবে সেই অংশটা এতই নগণ্য যে তা নিয়ে কখনও প্রশ্নের মুখে পড়তে হবে ভাবিনি। নয়ের দশকের শেষের দিকে জীবনানন্দের কাব্যে নানান আবিষ্কারের আলো এসে পড়ছিল, যার ফলে তখন জীবনানন্দের প্রাসঙ্গিকতা আমাদের কাছেও বিশেষ প্রাধান্য পাচ্ছিল। আমার ধারণা, তরুণ কবিদের ওপর অত বড় একজন কবির প্রভাব পড়াটাই সুস্থতার লক্ষণ। তাছাড়া আমরা দেখেছি গত শতাব্দীর পাঁচের দশকের অধিকাংশ প্রধান কবির লেখায় জীবনানন্দ অনুসারী হবার প্রবণতা স্পষ্ট। শক্তি বিনয় উৎপল এই তিন প্রধান কবিই ভাষাগত দিক থেকে এবং আংশিকভাবে ভাবের দিক থেকেও, স্পষ্টতই জীবনানন্দ অনুসারী। আগুন থেকেই তো আগুন জ্বলে। আর বিনয়ের কবিতা বিষয়ে আমাদের বিশেষ শ্রদ্ধা তখনও ছিল, এখনও আছে। এই পর্যন্ত অভিযোগকারীদের সঙ্গে আমি একমত।
অভিযোগটির নগণ্যতার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই এইবার। যারা অভিযোগটি করেন, তারা তাদের আংশিক অভিজ্ঞতার ঝুলিতে এই খবরগুলি সংগ্রহে রাখতে ভুলে গেছেন যে ‘গান্ধার’ পত্রিকা গোষ্ঠীর অধিকাংশ সদস্য শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতায়, উৎপলকুমার বসুর কবিতায় গভীর ভাবে আচ্ছন্ন থেকেছে দীর্ঘকাল। আরও একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিতে চাই এই প্রসঙ্গে। কফি হাউসের ওই আড্ডায় যোগ দেওয়ার পরেই আমি জানতে পারি যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও একজন বড় কবি, অবশ্যমান্য কবি। তার আগে পর্যন্ত তো আধুনিকতার ধ্বজাধারীরা আমাদের কানে অনবরত মন্ত্র দিয়ে চলতেন যে রবীন্দ্রনাথ অনাধুনিক, তার কাব্যে আধুনিক জীবনের ঘাত-প্রতিঘাত নেই, উনি বুর্জোয়া, জমিদার বাড়ির ছেলে, ক্ষুধার্ত সর্বহারা মানুষের জীবন থেকে তাঁর জীবন দর্শন অনেক দূরবর্তী... এইসব... সুতরাং গান্ধারের কবিগোষ্ঠী যে শুধু জীবনানন্দ দাশ বা বিনয় মজুমদারের অনুগামী ছিল তা একেবারেই নয়, তাদের চেতনায় বাংলা তথা বিশ্বসাহিত্যের বহু শ্রেষ্ঠ কবির প্রভাবই কাজ করেছে। কিন্তু সবকিছুর পরেও বলছি, কবিতা কোনও দলগত কাজ নয়। হয়তো সেকারণেই আমাদের গোষ্ঠীটিও অবলুপ্ত হয়েছে একদিন। না কোনও ঝঞ্ঝাট ঝামেলা নয়। অয়ন চক্রবর্তী ছিল তখন ওই আড্ডার প্রধান পৃষ্ঠপোষক। অয়ন ব্যস্ত হয়ে পড়ল সাংবাদিকতার কাজে। অন্যান্যরাও জীবিকার তাড়না অনুভব করল একে একে। ফলে সেই আড্ডা নিয়মিত ধরে রাখার মতো পরিস্থিতি আর রইল না। যদিও তার রেশ, একটা টেবিল ঘিরে এখনও আছে, কিন্তু তা আর আগের মতো কবিতাপ্রধান আড্ডা নয় মোটই।
দলের কথা তো গেল, এবার নিজের দু’একটা কথা বলি। আমি বাংলা কাব্যে চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি মধুসূদন রবীন্দ্রনাথ জীবনানন্দ সুধীন্দ্রনাথ শক্তি বিনয় যুগান্তর পার্থপ্রতিম প্রমুখ এবং বিশ্ব কবিতায় রুমি, জিব্রান, কিটস্, ব্লেক, ইয়েটস্, হুইটম্যান, পুশকিন, বোদলেয়ার, রিলকে, পাস্তেরনাক, ফ্রস্ট, হিমেনেথ প্রমুখ কবির কবিতার অনুসারী। আমার প্রভাবিত হওয়ার ধরনটি সর্বগ্রাসী। পৃথিবীর যে কোনও শ্রেষ্ঠ কবির দ্বারা, এমনকী অন্যান্য শিল্পমাধ্যমের শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার জন্য আমার মন সবসময়ই উদগ্রীব হয়ে থাকে।
প্রশ্ন ১১)কবিতা লিখে রাষ্ট্রের পুরস্কার বা পত্রিকা গোষ্ঠির পুরস্কার, এগুলো নিয়ে কী ভাবো?
উত্তর—পুরস্কার নিয়ে এখন আর কিছুই ভাবি না। আগে একসময় ভাবতাম, যখন মনে করতাম, কবিতায় পুরস্কার দেওয়া হয় ভালো লেখার জন্য। কিন্তু দীর্ঘদিন যাবত এইসব রাষ্টীয় এবং পত্রিকাগোষ্ঠীসমূহের দেওয়া পুরস্কারের সার্কাস দেখতে দেখতে আমার স্থির বিশ্বাস জন্মেছে যে ভালো লেখার জন্য কোনও পুরস্কারই দেওয়া হয় না আদৌ, তার পেছনে অন্য নানান সমীকরণ কাজ করে। রাজনৈতিক দল বা ক্ষমতাবান ব্যক্তির তাঁবেদারি না করে, আমাদের রাজ্যে বা দেশে, কেউ কোনও পুরস্কারই পায় বলে আমার মনে হয় না। কেউ কেউ যদি দৈবাৎ পেয়েও যায় বা যান, সেটা একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যতিক্রম বলে ধার্য হওয়া উচিত। সুতরাং কেউ পুরস্কার পেলেও পেল, না পেলে না পেল, নিলেও নিল, না নিলে না নিল, ব্যাপারটা এইরকম। কেননা পুরস্কার ব্যাপারটা এতোই বাহ্যিক যে সেটা নিয়ে না ভাবলেও কবিতা লেখার ক্ষেত্রে কোনও ক্ষতিবৃদ্ধি নেই।
প্রশ্ন ১২) তোমার নিজের লেখা সম্বন্ধে তোমার কী মনে হয়, মানে নিজের ক্ষমতা নিয়ে, সীমাবদ্ধতা নিয়ে কিছু ভেবেছ?
উত্তর—নিজের ক্ষমতা নিয়ে নিজে মুখে কিছু বলার ইচ্ছে আমার নেই। কারণ আমি আগেই বলেছি, কবিতা আমি লিখিনা, বরং কবিতাই আমাকে রচনা করে স্বয়ং। আমার কাজ আধার হিসেবে নিজেকে নিমগ্ন রাখা। সেটা হতে পারে প্রকৃতির নিবিড় সান্নিধ্যের মাধ্যমে, আগ্রাসী কবিতা পাঠের মাধ্যমে, অন্যান্য পড়াশুনোর মাধ্যমে, ছন্দ শিক্ষার মাধ্যমে, গান শোনার মাধ্যমে, ফুটপাথে ফুটপাথে অকারণ ঘুরে ফেরার মাধ্যমে, মানুষের সঙ্গে মেলামেশার মাধ্যমে, নিভৃত কোনও অবকাশে আত্ম-উপলব্ধির মাধ্যমে, আত্মবিলোপের মাধ্যমে। সেই প্রসঙ্গে আজ এটা নির্দ্বিধায় বলতে পারি, এখনও পর্যন্ত আমার কবিতাজীবনে সীমাবদ্ধতা বিপুল। জীবন যে অফুরন্ত ভাণ্ডার আমার সামনে মেলে ধরেছে এযাবৎকাল, তার খুব কম অংশই আমি সার্থক কবিতা হিসেবে ধরে রাখতে পেরেছি। আসলে কবিতার জন্য যে সমর্পণের জীবন দরকার, তা আমি গত কয়েকবছর সার্বিকভাবে যাপন করে উঠতে পারছি না। জীবিকার তাড়নাতেই জীবনের অনেকটা ফুরিয়ে যাচ্ছে। লিখেওছি সেই কথা। ‘স্বপ্নে আগুনের মন্ত্র দিয়েছিলে / জ্বালানি কুড়োতেই জীবন জেরবার’। ফলে আধার হিসেবে নিজেকে সবসময় টনটনে সজাগ রাখার অবকাশ না পাওয়া, আমার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় সীমাবদ্ধতা এখন। আগে বহুদিন সেই যাপন করতে পেরেছি, ভবিষ্যতেও পারব আশা রাখি। তখন এই বর্তমান সীমাবদ্ধতাও অনেকটা কাটিয়ে উঠতে পারব, আমার ধারণা। অন্তত কাটিয়ে ওঠার আপ্রাণ চেষ্টা তো করবই। দেখা যাক জীবন সেই সুযোগ আমাকে আদৌ দেয় কিনা, বা দিলেও, কবে দেয়।
মতামত ব্যক্তিগত
উত্তর— আক্ষরিক অর্থে কবিতা লেখা শুরুরও বেশ কয়েকবছর আগে, খেলাচ্ছলে কিছু প্রেমপত্র লিখতে গিয়ে আমি টের পাই, সেই কৃত্রিম লেখাগুলোর ভেতর দিয়েও, আমার যোগ্যতার অতিরিক্ত কিছু সৌন্দর্য ও সুষমা, আমার সম্পূর্ণ অবচেতনেই প্রকাশিত হয়ে পড়ছে। সেসব চিঠি যে শুধু নিজের জন্যই লিখতাম তা নয়, বরং বন্ধুবান্ধব অনেকের বকলমেই সেই পাপ আমি করেছি। করতে করতে এক বিপজ্জনক খেলায় নিজেও জড়িয়ে পড়েছি। ১৭/১৮ বছরের উন্মত্ত কৈশোরে জড়িয়ে পড়েছি ফিল্মি আবেগ নির্ভর মিথ্যে প্রেমের যন্ত্রণাদায়ক সম্পর্কে। কম বয়সের মোহে সেই সম্পর্কের রেশ টেনেছি বছর তিনেক। তারপর যথারীতি তা একদিন ফুরিয়ে যাবার সময় এসেছে। দু’জনের পথ, প্রাকৃতিকভাবেই পৃথক হয়ে পড়েছে একদিন। কিন্তু ফর্মুলাবদ্ধ সমাজের চোখে ঘোরতর অন্যায় হয়ে দাঁড়াল সেই বিচ্ছেদ। পাড়া প্রতিবেশী থেকে শুরু করে আমার আত্মীয় বন্ধু প্রায় সকলেই সেই বিচ্ছেদের জন্য আমার অপদার্থতা আর সামাজিক অযোগ্যতাকেই দায়ী করতে থাকল। আমি ভয়াবহভাবে একা হয়ে গেলাম। এমনকী আমার বাড়ির লোকেরাও সে সময় আমাকে করুণার চোখেই দেখতে শুরু করেছিল। তখন আমি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিষয়ে স্নাতকস্তরের ছাত্র। দিনের বেলা কলেজ সেরে, বাড়ি ফিরতাম বিকেলে। তারপর সন্ধে অব্দি বালিশে মুখ গুঁজে পড়ে থাকতাম, যতক্ষণ না অন্ধকার নেমে আসে চারপাশে। দিনের বেলা আলোয় বাড়ির বাইরে বেরতে আমার ইচ্ছেই করত না। আমিও কারুর মুখ দেখতে চাইতাম না, অন্য কেউ আমাকে দেখুক তাও চাইতাম না। সন্ধের আবছায়ায় বাড়ি থেকে বেরিয়ে হাঁটতে হাঁটতে প্রায় চল্লিশ মিনিটের পথ পেরিয়ে পৌঁছতাম পাটুলি সংলগ্ন বাইপাসের ধারে। তখন সবে নির্মিয়মান বাইপাসের ধারগুলোয় শুধু অন্তহীন মাছের ভেড়ি। ভেড়ির পর ভেড়ি। দুটো ভেড়ির মাঝ বরাবর চলে গেছে সরু সরু আলপথের মতো রাস্তা, মিশে গেছে দূরের ঘন অন্ধকারে। এখন যেখানে ‘বেণুবনছায়া’, সেখানে তখন নিশ্ছিদ্র কুয়াশাঘন অন্ধকার, জলায় জলায় জমাট বেঁধে থাকত। পুবদিকের অন্ধকার চিরে শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখার ট্রেন চলে যেত গড়িয়া স্টেশনের দিকে। তারপর সোনার থালার মতো চাঁদ উঠত রেললাইনের উত্তর-পূর্ব কোণ থেকে। আমি একা জলের ধারে বসে থাকতাম ঘন্টার পর ঘন্টা, সন্ধের পর সন্ধে। বসে বসে দেখতাম কালো জলের ওপর কেমন ঝাঁপিয়ে পড়েছে ঝকঝকে তারায় ভরা রাত্রির আকাশ। দূরে, আলপথের কুয়াশা ভেদ করে, চাদর জড়ানো দিনমজুরের দল বিড়ি টানতে টানতে চলে যাচ্ছে ক্রমাগত রেললাইনের দিকটায়… সেইসময় নিজের অজান্তেই আমি ধ্যানস্থ হয়ে পড়তাম যেন। সেই নির্জন, নৈসর্গিক অন্ধকারে, তারায় ভরা অন্তহীন আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে আমার একবিন্দু প্রাণ যেন এক মহাজাগতিক জীবনের ইশারা অনুভব করত। বেশ কিছুদিন এইরকম চলার পর বুঝলাম, অনেক অনেক কথা যেন জমা হচ্ছে আমার ভেতরে, কিন্তু সেইসমস্ত আকাশকুসুম ভাব প্রকাশের ভাষা যে আমি জানি না। বুকের ভেতর কী যে জমাট সেই অবস্থা, আজও বলে বোঝানো সম্ভব নয়। তাছাড়া সেইসব কথার ভাব এমনই, যে তা ভাষায় যদি প্রকাশ করাও যায়, শুনবেটা কে? এই বিশ্বচরাচরে আমার পরিচিত এমন কোনও মানুষের মুখ তখন মনে পড়ত না, যাকে গিয়ে আমার মনের কথা বলতে পারি। সেই কথা কিন্তু কোনও সম্পর্ক ভাঙার কাঁদুনিমাত্র নয় মোটেই। ফেলে আসা সম্পর্কের সঙ্গে তার কোনও সম্পর্ক প্রায় নেই বললেই চলে, বরং সেইসমস্ত কথা যেন আমার এই একলা হয়ে পড়ার অপেক্ষাতেই বুকের ভেতর নির্মমভাবে ঘাপটি মেরে ছিল এতকাল। ক্রমান্বয়ে সেই কথাগুলোই আমাকে চাপ দিতে থাকল লেখার। গর্ভস্থ শিশু যেমন প্রসবের জন্য মায়ের পেটে চাপ দেয়, সেইরকমই অনেকটা। একটা দুটো লেখার সূত্রপাত হয় তখনই। কিন্তু কবিতা লেখা তো দূর, সমসাময়িক কবিতা পড়ার দীক্ষাও তো তখন আমার ছিল না, ফলে কাঁচা ভাষায় অনিয়ন্ত্রিত আবেগের স্রোত বয়ে যেত সেসব লেখার ভেতর দিয়ে। তখন এক বন্ধু আমায় একদিন ‘জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা’ বইটা ওদের পারিবারিক সংগ্রহ থেকে দেখাল। ওর এক পিসিকে সেই বই উপহার দিয়েছিলেন স্বয়ং লাবণ্য দাশ। উপহারের পাতায় তার ‘নির্জন স্বাক্ষর’ দেখে খুবই শিহরিত হয়েছিলাম, মনে আছে। সেই আমার প্রথম, পাঠক্রমের বাইরে, জীবনানন্দ পড়ার শুরু। তার কিছুদিনের মধ্যেই ঈশ্বরের কৃপায়, আর দু’একজন বন্ধুর সাহয্যে হাতে এল ‘শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা’, বিনয় মজুমদারের ‘ফিরে এসো চাকা’, ‘উৎপল কুমার বসুর শ্রেষ্ঠ কবিতা’(কবিতা সংগ্রহেরও অনেক আগে বেরিয়েছিল)… এইসব। ফলে জীবনানন্দ পরবর্তী বাংলা কবিতা সম্পর্কে একটা প্রাথমিক ধারণা হলো আমার। তখন একদিন জানলাম, আমাদের পাড়ার বাপ্পা দা নাকি এই সময়কার (নয়ের দশকের) একজন উজ্জ্বল কবিতাপ্রয়াসী। পোশাকি নাম যার সন্দীপ চট্টোপাধ্যায়। গেলাম ওর কাছে। ও তখন একটা বিশাল উপকার করেছিল আমার। বলেছিল, হাজার বছরের বাংলা কবিতায় নিয়মনিষ্ঠ ছন্দের ভূমিকার কথা। উৎসাহ দিয়েছিল ছন্দ শেখার। সেটা ৯৫ সাল হবে। আমি ছন্দ শেখায় যত্নবান হলাম। সেসময় নয়ের দশকের এক ব্যতিক্রমী উজ্জ্বল তরূণ-কবি দীপঙ্কর বাগচীর সঙ্গে আমার আলাপ। ওর কাছেও ছন্দ এবং কবিতা বিষয়ক কিছু সাহায্য তখন পেয়েছি। এর পরের দু-তিন বছর, ছন্দ শিখতে শিখতে যাকিছু লিখেছি, তার কিছুই আর পরবর্তী সময় কোথাও রাখিনি, কারণ আমি কীভাবে যেন বুঝে ফেলেছিলাম-- কবিতার চেহারা আর কবিতা এক জিনিস নয়। সেটাই ছিল আমার কবিতা-জীবনের প্রথম এবং কঠিনতম পরীক্ষা। ছন্দে লিখব, কিন্তু ছন্দ লিখব না, লিখব বিশুদ্ধ কবিতা। সেই পরীক্ষা বা সাধনার প্রথম সিদ্ধাই আমার প্রথম কবিতার বই ‘ব্যক্তিগত আলেখ্যের প্রতি’। রচনাকাল ৯৮, ৯৯ । এই সময়কালেই আমি স্পষ্ট করে টের পাই, কবিতা আমি লিখি না, বরং আমাকে রচনা করে কবিতা স্বয়ং। বুকের ভেতর জমাট হয়ে থাকা কথাগুলো কেমন যেন আপনাআপনি ছন্দবদ্ধ হয়ে আমার কলমের ডগায় নেমে আসে প্ল্যানচেটের মতো। সেইসময়কার আদিতম রচনাটির অংশবিশেষ ছিল এইরকম—
‘কবিতার দোষে আমি কাপালিক হয়ে যেতে পারি। / যে দেহ শব্দের লাশে ব্যোম হয়ে ছুঁয়েছে স্তব্ধতা, / গোপন পাঁজরে আজ স্বীকার করেছি যার কথা, / আগুন যজ্ঞের নীচে পুড়ে যাওয়া সে দেহ আমারই...
...কবিতার দোষে আমি কাপালিক হয়ে যেতে পারি / অর্থাৎ কবিতা লিখে কবি হতে পারিনা কক্ষনো...
যা কিছু রচনা নয়, ততটাই লিখে রাখা চলে; / যেমন আড়াল গেঁথে, হয়তো কেউ তাকে স্পর্ধা বলে।’
এই লেখাটির সূত্র ধরেই একদিন নয়ের দশকের অন্যতম প্রধান কবি অনির্বাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমার আলাপ এবং সেই সূত্রেই কলেজস্ট্রিট কফিহাউসের ‘গান্ধার’ পত্রিকাগোষ্ঠীর বন্ধুদের সঙ্গে মেলামেশার সূত্রপাত। অনেকটা এইরকমই আমার কবিতা লেখা শুরুর দিনগুলো।
প্রশ্ন ২) তুমি তো উচ্চাঙ্গসঙ্গীত পছন্দ করো, এই অভ্যেসটা কী করে হলো?
উত্তর-- সুরের প্রতি অনুরাগ আমি পেয়েছি মামাবাড়ির সূত্রে। মা-মাসিদের গানের গলা ছিল বড্ড সুরেলা। যে-সমস্ত গায়ক গায়িকার গলায় ধ্রুপদী দক্ষতা বেশি, তাঁদের বিশেষ ভক্ত ছিল আমার মা-মামা-মাসিরা সবাই। তাছাড়া আমার বাড়ির ঠিক উল্টোদিকের বাড়িতেই ছিল একটা গানের স্কুল। সারা বিকেল-সন্ধে জুড়ে নানান রাগরাগিণীর তালিম চলত। আমি যে খুব মন দিয়ে শুনতাম তা নয়, কিন্তু পরবর্তী সময় দেখেছি সেইসব সুর আমার অবচেতনে কেমন অলৌকিকভাবেই সঞ্চিত হয়ে থেকে গিয়েছিল। ওই যে একলা দিনগুলোর কথা বলছিলাম, সেই সময়ই একদিন ঘুরতে ঘুরতে আমি ঢুকে পড়েছিলাম ‘দক্ষিণী সঙ্গীত সম্মেলন’-এর বার্ষিক আসরে। টালিগঞ্জে, আমার বাড়ির কাছে, সেই আসর এখনো বসে প্রতি জানুয়ারির ৮/১০ তারিখ নাগাদ। প্রায় চল্লিশ বছর ধরে বসছে। সেই যে একবার ঢুকে পড়লাম, তারপর থেকে গত বাইশ-তেইশ বছর যাবত আমি ঘোরতর আসক্ত হয়ে আছি ভারতীয় সঙ্গীতের অলৌকিক সৌন্দর্যময় ঐশ্বর্যে। কিছু কিছু রাগরাগিণী, উপযুক্ত পরিবেশনায় শুনে মনে হয়েছে এই সুর তো আমার বহুকালের চেনা। সেই চেনার বয়সকাল যেন বা আমার তৎকালীন বয়সের তুলনায় অনেকগুন বেশি। যেন কয়েক জন্মান্তরের ব্যবধান। উস্তাদ ফৈয়াজ খাঁ সাহেবের গাওয়া দেশ রাগ শুনে, বিদুষী মালিনী রাজুরকারের জৌনপুরি শুনে, বিদুষী কিশোরী আমনকারের বাগেশ্রী শুনে এই অনুভূতি আমার বারবার হয়েছে। এসব নিয়ে বেশ কিছু কবিতাও আমি বিভিন্ন সময় লিখেছি। জন্মান্তরের আখ্যানগুলো, বৃহত্তর অর্থে সঙ্গীত শোনার আগে পর্যন্ত আমার কাছে গল্প বলেই মনে হতো, এমনকী জাতকের কাহিনীও। কিন্তু ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত আমাকে জন্মান্তরের স্পষ্ট আভাস দিয়েছে। আমি জীবনে প্রথম বেনারস যাবার অন্তত ১৫/২০ বছর আগে থেকেই গভীরভাবে অনুভব করেছি যে বেনারসের সঙ্গে আমার জন্মান্তরের কোনও না কোনও যোগাযোগ আছে। সেই টান ব্যাখ্যাতীত। আমার ‘যে আরতি মণিকর্ণিকার’ বইটিতে সেই বিস্ময় আংশিকভাবে লিপিবদ্ধ।
বছর কুড়ি আগে যখন ডোভার লেন সহ অন্যান্য মিউজিক কনফারেন্স শোনা শুরু করি, টিকিট কাটারও পয়সা থাকত না। এর-তার থেকে টিকিট বা পাস জোগাড় করে কোনোক্রমে ঢুকতাম। সারারাত খিদের জ্বালায় ছটফট করতে করতেও গোগ্রাসে গানবাজনা শুনতাম, কিন্তু কিছু কিনে যে খাব, তার উপায় কোথায়? পকেট যে গড়ের মাঠ। আমার গানবাজনা শোনার দীর্ঘদিনের সঙ্গী স্বর্ণেন্দু সরকার তেমনই অনেক অসহায় এবং আনন্দঘন রাত্তিরে আমার প্রাণ বাঁচিয়েছে খাইয়েদাইয়ে। তবু সঙ্গীতের ওপর আমার আসক্তি দিন-কে-দিন বেড়েছে বৈ কমেনি। জন্ম থেকেই আমার গলায় সুর ছিল পর্যাপ্ত, মায়ের তাই ইচ্ছে ছিল গান শেখানোর, কিন্তু বাবার একার রোজগারে আর সেটা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। তবুও যত দিন গেছে, আমি সঙ্গীতের প্রেমে হাবুডুবু খেয়েছি ততই। আজ অনুভব করি, আমার লেখার পেছনেও সেই সঙ্গীত-প্রেমের ভূমিকা অপরিসীম। শব্দ বা বাক্যে প্রাণসঞ্চার করার ক্ষেত্রে সুরের ভূমিকা খুবই অলৌকিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। তাছাড়া সঙ্গীত-প্রীতির হাত ধরেই আমি ক্রমশ আচ্ছন্ন হয়েছি অধ্যাত্মবাদে। অনুভব করেছি, সঙ্গীত, ঈশ্বরের সঙ্গে কথোপকথনের শ্রেষ্ঠ এবং সূক্ষ্মতম পথ। আমরা তো গৃহী মানুষ, খাঁটি সাধু বা সাধক দেখার সুযোগ আমাদের খুবই কম, কিন্তু সঙ্গীতই আমার জীবনে সেই পরিসর, যা আমাকে শিখিয়েছে সাধক চিনতে। সাধনা বস্তুটিও ঠিক কী জিনিস আমি বুঝতে শিখেছি সেইসব সাধক শিল্পীদের দেখেই। আরো একটা ব্যাপার, আমাদের সমাজে যে সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়ানো রয়েছে বহুকাল যাবত, যা অবচেতনে বেশিরভাগ মানুষকেই আচ্ছন্ন করে রেখেছে, তার হাত থেকেও আমি চিরতরে মুক্তি পেয়েছি উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতেরই কৃপায়। বাবা আলাউদ্দিন খাঁ, পণ্ডিত ভাস্কর বুয়া বাখলে, উস্তাদ আব্দুল করিম খাঁ, উস্তাদ বিসমিল্লা খাঁর জীবনকথা, আমাকে এই অভিশপ্ত সাম্প্রদায়িক সমাজ থেকে বহুদূরের এক জন্নতে পাকাপাকিভাবে অধিষ্ঠিত করেছে, সম্ভবত বাকি সারা জীবনের জন্য।
এখন আমার মেয়ে সেতার শিখছে, আমি চাই ওর জীবনে, ওর সমগ্র জীবনব্যাপী, সঙ্গীত যেন প্রত্যক্ষভাবে ক্রিয়াশীল হয়, ক্রিয়াশীল থাকে। তাহলে আমার সঙ্গীত-প্রেম আরোই অর্থবহ হয়ে উঠবে আশা করি। আমি তো ঈশ্বর বিশ্বাসী, তাই মাঝে মাঝে ভাবি, হয়তো আমার মেয়ে একদিন প্রত্যক্ষ সঙ্গীতচর্চা করবে বলেই পরম রহস্যময়, করুণাময় ঈশ্বর আমাকে এত বছর ধরে পাক খাইয়েছেন এত অজস্র আসরে, মজলিশে।
প্রশ্ন ৩) গানের কথা আর কবিতার কথার মধ্যে ফারাক করবে? করলে সেটা কী?
উত্তর— গানের কথা অনেক ক্ষেত্রে কাব্য হয়ে উঠতেই পারে, যেমন কবীর-লালন-রবীন্দ্রনাথ কিংবা কবীর সুমনের বহু গান, কিন্তু তা সত্বেও গানের কথা আর কবিতার কথা সমার্থক নয় কিছুতেই। মনে রাখতে হবে, যে-গানকে সূক্ষ্মতম শিল্পের মর্যাদা দেওয়া হয়ে থাকে, তা মূলত সুরপ্রধান। কথা সম্বলিত গান সেই জায়গা কোনোদিনই দাবী করতে পারে না। সেটা একটা মিথোজীবী শিল্প। একে অন্যের ওপর নির্ভরশীল। কথা লিখতে গেলে সুরের কথা, সুর করতে গেলে কথার কথা মাথায় না রেখে উপায় থাকে না। কিন্তু কবিতা তার তুলনায় অনেক স্বাধীন। ছন্দের ছাঁচও যে কবিকে মানতেই হবে, তেমনও কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। সারাজীবন ছন্দে না লিখেও কেউ ওয়াল্ট হুইটম্যানের মতো চিরস্মরণীয় কবি হতেই পারেন। এমনকী গীতি-কবিতার ক্ষেত্রেও যে গীতলতা, সেও কিন্তু সুরের ভরসায় থাকে না। আবার দ্যাখো, গানের কথায় কখনোই ভারী শব্দের ব্যবহার বা ভাবের অতিরিক্ত বিমূর্ততা কাম্য নয়, সেক্ষেত্রেও কবিতার পক্ষে অনেকটাই স্বাধীনচেতা, স্বেচ্ছাচারী হওয়া সম্ভব।
প্রশ্ন ৪) তোমার কবিতা ভাবনায় একটা ধ্রুপদী চিন্তন লক্ষ করা যায়। এই ব্যাপারটা এল কীভাবে? মানে নয়ের দশকে যখন সশব্দ হাততালির কবিতা বাহবা পাচ্ছে, তখন তুমি সেদিকে না গিয়ে থাকলে কী করে?
উত্তর-- কবিতা লেখার অন্যতম শর্ত হিসেবে একজন কবিকে প্রথমে একজন শ্রেষ্ঠ কবিতা-পাঠক হয়ে উঠতে হয়। এই কবিতা পাঠের মধ্যে দিয়েই গড়ে ওঠে তার ব্যক্তিগত কাব্য সংস্কার। আমি যখন বাংলা কবিতা বা বিশ্ব-কবিতার পাঠ নিতে শুরু করেছি, তখন থেকেই লক্ষ করতাম, যাঁদের যাঁদের কবিতা আমার ভালো লাগে তাঁদের মধ্যে একটা গভীর সাদৃশ্য আছে কোথাও যেন। সেই সাদৃশ্যটি হলো ওই Sense of eternity বা শাশ্বতের ধারণা। হয়তো সেসব বিভিন্ন কবির বাহ্যিক জীবনযাপন, এমনকী কবিতার ভাষা একেবারেই আলাদা। কেউ ধরো খুব শান্ত, স্থিতধী, যেমন রবীন্দ্রনাথ বা রিলকে… আবার কেউ বেদম উন্মত্ত, উড়নচণ্ডী, যেমন বোদলেয়ার বা মধুসূদন… কিন্তু এই সমস্ত কবিকেই যে একই সঙ্গে আমার প্রাণে ধরল, তার প্রধান কারণ ওই মহাজাগতিক চিরন্তনতার বোধ, যা থেকে প্রকাশ পায় বিশ্বমানবতার আবহমান চেতনা। তার পাশাপাশি লক্ষ করে দেখলাম, যে আমার প্রিয় কবিদের সকলেরই কবিতায় আছে আশ্চর্য মন্ত্রশক্তি। খুব সম্ভব ওই চিরন্তনতার বোধের সঙ্গে এই মন্ত্রশক্তির একটা ব্যাখ্যাতীত সম্পর্ক আছে। মধুসূদন-রবীন্দ্রনাথ থেকে জীবনানন্দ-সুধীন্দ্রনাথ, রুমি-হাফিজ থেকে জিব্রান-গালিব কিংবা কীট্স্-ব্লেক থেকে ইয়েট্স্-ফ্রস্ট সকলের মধ্যেই ওই দু’টি জিনিসের আশ্চর্য সম্মেলন আমি লক্ষ করেছি অতি যত্নসহকারে। আর সেখান থেকেই আমার মধ্যে ‘ধ্রুপদী চিন্তন’-এর সূত্রপাত হয়তোবা। তারই দাবী অনুযায়ী আমি কবিতা লেখার প্রায় শুরু থেকেই ধ্রুপদী আঙ্গিকের চর্চাও সযত্নেই করেছি। আমার সামান্য সংখ্যক পাঠকমাত্রেই জানেন যে আমি সনেট বা চতুর্দশপদী কবিতায় সবিশেষ অনুরক্ত। তবে প্রিয় কবিতা বাছার ক্ষেত্রে আমি ধ্রুপদী আঙ্গিকের চেয়ে ধ্রুপদী ভাবনাকেই বেশি প্রাধান্য দিই, যার জন্য ওয়াল্ট হুইটম্যানও আমার প্রিয় কবিদের অন্যতম। ঠিক যেমন করে হিমেনেথের ‘Platero and I’ আমার অন্যতম প্রিয় কবিতার বই।
যেহেতু আমি কবিতার ব্যাপারে ভয়ানক সংস্কারাচ্ছন্ন, নাকউঁচু, তাই আমার সমসময়ের অধিকাংশ কবি এবং কবিতাকে আমি করুণাই করে এসেছি চিরকাল। যতই তারা হাততালি পান, যতই তারা বগল বাজান মিডিয়ায়, আমি ফিরে দেখারও প্রয়োজন বোধ করিনি। আমার খুব সৌভাগ্য যে অল্প হলেও আমার সমসময়ে আমি এমন কয়েকজন কবিবন্ধুকে পেয়েছি যারা কবিতার ব্যাপারে আমার মতোই বা আমার চেয়েও বেশি সংস্কারাচ্ছন্ন, আমার মতোই, তারাও ধ্রুপদী চিন্তনে ধারাবাহিক আস্থা রেখে আসছে। সেই সূত্রেই হয়তো কাছাকাছি আসার সুযোগ হয়েছিল আমাদের, যার ফলে পারস্পরিক ভাব বিনিময়ের মাধ্যমে লাভ হয়েছে হয়তো সবারই।
প্রশ্ন ৫) তোমার দশকের কবিতা নিয়ে তোমার মতামত কী?
উত্তর— অন্যান্য দশকের মতোই, নয়ের দশকের কবিতাকেও আমি স্পষ্ট দুটো ধারায় ভাগ করতে পারি। একদল গোড়া থেকেই দাদা-ধরা, প্রতিষ্ঠানমুখী, যশলোলুপ। নাচন-কোঁদন যা কিছু করেই হোক না কেন, নাম তাদের করতেই হবে। তাই তারা প্রথম থেকেই খাঁটি কবিতার ধারেকাছে ঘেঁষেনি কোনও দিন। বরং কবিতার শরীর ধার নিয়ে তারা লিখেছে সমসাময়িক বাজার অনুমোদিত চলতি-বিষয় এবং চালু-ভাষা অবলম্বনে বিচিত্র কিছু ছড়া। যেহেতু যোগ্যতার পরিবর্তে তাদের যোগাযোগ দক্ষতাই ছিল প্রধান সম্বল, তাই তেলখোর দাদাবাবুদের কাছে তাদের গ্রহণযোগ্যতাই ছিল বেশি। সময় মতো তারা তার স্বীকৃতিও পেয়েছে। নয়ের দশকের প্রধান কবি হিসেবে তাদেরকেই চিনেছেন সাধারণ অভাগা মানুষ।
অথচ এই নয়ের দশকেই লেখা হয়েছে এমন কিছু কবিতার বই, যার যথাযোগ্য সংকলন হলে জীবনানন্দ পরবর্তী বাংলা কবিতার ধারণা অনেকটাই বদলে যেতে পারে। যেসমস্ত কবিতার বই, তুমি চাইলে, পৃথিবীর যে কোনও সেরা কবিতার বইয়ের পাশাপাশি রেখেও পড়তে পারো। সেইসমস্ত অনামজাদা কবি, নিজেদের মনের আনন্দে মগ্ন হয়েই কবিতা লিখে চলেছে এখনও। ক্ষমতাবান দাদা-বাবুরা তাদের নানান লোভ দেখিয়েও বশে আনতে পারেননি। অথচ সেই বাবুসমাজ প্রবলভাবে চেয়েছিলেন, নিজেদের সাম্রাজ্য দীর্ঘস্থায়ী করার খাতিরে এইসমস্ত শক্তিশালী পথের কাঁটা যেনতেন ভাবে সরিয়ে ফেলতে। তার জন্য তাঁদের উদ্যোগের কোনও অভাবও ছিল না। তারপরেও তাঁরা বিশেষ পাত্তা তো পানইনি বরং উপেক্ষিতই হয়েছেন বারবার। তাই তাঁরা তাঁদের ছেড়ে যাওয়া সিংহাসনে এমন কিছু বন্ধ্যা ছড়াকারকেই বসিয়েছেন, যারা হাজার বছর রাজা হয়ে বসে থাকলেও পূর্ববর্তী সম্রাটের প্রভাব লঘু হবে না একফোঁটাও।
কিন্তু আমি বলি কী, এইসব ছকবাজি তো আজকের নতুন ব্যাপার নয়, তারপরেও জীবনানন্দ দাশ, বিনয় মজুমদার, শম্ভুনাথ চট্টোপাধ্যায়, তুষার রায়, পার্থপ্রতিম কাঞ্জিলালদের কোনোভাবেই আটকে দেওয়া গেছে কি? নয়ের দশকের অনালোচিত কবিদের মধ্যে অন্তত এমন তিনজন এখনও লেখার ভেতর আছে, যারা নিজেদের সমকালীন কাব্য-ইতিহাস নতুন করে লিখতে বাধ্য করবে একদিন। কারণ আমি যাদের কথা বলছি, তাদের লেখায় রয়েছে সেই অতিদুর্লভ Sense of eternity, যা খাঁটি কবিকে, মৃত্যুর ২০০ বছর পরেও আবার নতুন করে বাঁচিয়ে তুলতে পারে। উল্টোদিকে, সমসাময়িক উত্তেজনাপ্রসূত কবিতা, সময়ের সঙ্গে সঙ্গেই ফিকে হয়ে আসে আপনাআপনি।
প্রশ্ন ৬) পরবর্তী কবিদের লেখাকে কী চোখে দেখছ?
উত্তর— নয়ের দশকের কবিতা সম্পর্কে যা বললাম, তা শুধু নয়ের দশকেরই গল্প তো নয়, সাতের দশকেও এই একই গল্প ছিল, যা আজ সময়ের ব্যবধানে খুবই প্রকটভাবে পরিস্ফুট। কিন্তু নয়ের দশকে এসে সেই গল্পের প্যাটার্ন বদলেছে। আবার এই শতাব্দীর কবিদের মধ্যেও সেই একই ট্রেন্ড আমি লক্ষ করছি। একদল নির্লজ্জভাবে তেল দিচ্ছে প্রকাশ্যে, আবার একদল এসব থেকে সচেতনভাবেই দূরত্ব বজায় রেখে নিজেদের কবিতায় সাধনার পরিসরকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করে যাচ্ছে। নয়ের দশকের তুলনায় এই গল্পের প্যাটার্নও আবার বদলে গেছে অনেকটা। বিশেষত সোশ্যাল মিডিয়ার প্রভাবে আজকের এই প্যাটার্ন চেঞ্জ বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। যেমন তাৎপর্যপূর্ণ ছিল নয়ের দশকে কম্পিউটার এবং গ্লোবালাইজেশনের আবির্ভাব। কিন্তু যদি তুমি শাশ্বতের ধারণা থেকে বিষয়টা দ্যাখো, তাহলে দেখবে, খণ্ডচিত্রগুলোর বৈষম্য থাকা সত্ত্বেও আসলে মূল বিষয়টা থেকে গেছে একই। যোগ্যতার তুলনায় যোগাযোগ দক্ষতার কদর যে কোনও যুগেই বেশি। অথচ কবিতার ক্ষতিবৃদ্ধি হয়নি তাতে বিশেষ। ক্ষতি হয়েছে পাঠকের, পাঠরুচির। পাঠক নিজের সমকাল থেকে ক্রমশই পিছিয়ে পড়েছে এবং পড়ছে। সমকালীন শ্রেষ্ঠ কবির খোঁজ পাওয়ার আগেই ফুরিয়ে যাচ্ছে তার আহ্লাদের আয়ুষ্কাল।
প্রশ্ন ৭) সমসাময়িক রাজনীতি নিয়ে তোমার ভাবনার জায়গাটা ঠিক কী?
উত্তর— আমার এযাবৎ কথাবার্তা থেকে এটা নিশ্চয়ই বোঝা যাচ্ছে যে ‘সমকাল’ বিষয়টা আমার কাছে ‘চিরকাল’-কে চেনারই একটা উপকরণমাত্র। সমকালীন ভারতবর্ষ তথা বিশ্ব জুড়েই যে উগ্র সাম্প্রদায়িক রাজনীতির প্রকাশ দেখা যাচ্ছে, যুদ্ধের রাজনীতির প্রকাশ দেখা যাচ্ছে, নাক্ষত্রিক উচ্চতা থেকে দেখলে মনে হয় পৃথিবীতে এসব কোনও নতুন ঘটনাই নয়। এর মধ্যেও যা শাশ্বত, তা হচ্ছে একশ্রেণির শোষণ আর এক শ্রেণির শোষিত হওয়ার ইতিহাস, যার পুনরাবৃত্তি ঘটছে শতাব্দীর পর শতাব্দী, সভ্যতার পর সভ্যতাব্যাপী। সেই নিয়মেই মার খেতে খেতে আজও জেগে উঠছে দলিত সম্প্রদায়, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, আদিবাসী সম্প্রদায়... ধারাবাহিক আত্মহত্যার বিষাদ কাটিয়ে দীর্ঘতম মিছিল থেকে ডাক পাঠাচ্ছে কৃষকসমাজ... সমকালীন রাজনীতি আমাকে এমনই কিছু চিরকালীন বার্তা দিয়ে যায়, যা দলগত রাজনীতির ধারণা থেকে বহু দূরের ব্যাপার। সম্ভবত অন্য পৃথিবীর।
প্রশ্ন ৮) বিশ্ব-পরিস্থিতি, মানে প্যালেস্তাইন, গাজা, এসব তোমার লেখাকে প্রভাবিত করে?
উত্তর— এই প্রশ্নের উত্তরে একটা কবিতাই বরং উদ্ধৃত করতে চাই, তা থেকেই যা বোঝার বোঝা যাবে আমার ধারণা—
আতঙ্কবাদীকে লেখা চিঠি
আসুন আতঙ্কবাদী, পৃথিবীর ক্ষীণ শেষবেলায়
সিরিয়া ভারত ফ্রান্স বাংলাদেশ কিংবা কেনিয়ার
যেকোনও সূর্যাস্ত-প্রান্তে দু’মিনিট একটু বসা যাক;
লুটিয়ে ঘাসের গায়ে আগ্নেয়াস্ত্র, নিশ্চিন্তে বসুন।
দিনের ওপারে যায় দেখুন কীভাবে দিনমণি;
কীভাবে সমস্ত তেজ ত্যাগ-মন্ত্রে করে সম্বরণ;
কেননা তাকেও সরে যেতে হয়, রাতের হাতেই
সন্তানের, সভ্যতার, প্রতিপালনের ভার দিয়ে।
তিনি কি পারেন না নিজ-তেজে হতে আত্মঘাতী ছাই?
তিনি কি পারেন না রাগে অন্ধ হয়ে চির অন্ধকার
করে দিতে এ জগত? বিশেষত এই আমাদের
লোভ হিংসা ব্যাভিচারে রক্তারক্তি সংসার যখন...
তা তো তিনি করেন না কখনও; সে কি তেজের অভাব?
বরং সৃষ্টির ধর্ম এই তার, প্রেমধর্ম, স্নেহধর্ম এই...
তেজের মহিমা শুধু সম্বরণে হয় ফলপ্রদ;
ফলস্বরূপ সেই শিশু, আপনারও কি তেজঃবীর্যে নেই?
প্রশ্ন ৯) সাম্প্রতিককালে শঙ্খবাবু আর সুমনকে নিয়ে তোমার করা মন্তব্যে প্রচুর বাদ-বিবাদ হয়। এই দুই ব্যক্তিত্ব এবং তাদের কাজ বিষয়ে তোমার মতামত ঠিক কী?
উত্তর— শঙ্খ ঘোষ, একজন পণ্ডিত, প্রাবন্ধিক, সংবেদনশীল নাগরিক হিসেবে আমার কাছে বরাবরই শ্রদ্ধেয়। ওঁর বিষয়ে শুধু দুটো কথা বুঝতে আমার অসুবিধে হয়। প্রথমটি হল— শঙ্খ ঘোষের কবিতা। ‘দিনগুলি রাতগুলি’ বইটিতে আমি একজন সংবেদনশীল প্রেমিকের দেখা পাই, বৃহদর্থে ব্যথা পাই আনন্দ পাই তার ছোঁয়ায়। কিন্তু তার পর থেকেই আমি শঙ্খ ঘোষের কবিতায় পেতে শুরু করি সামাজ-শিক্ষার দায়িত্বপ্রাপ্ত একজন আচার্যকে। যিনি প্রচার করে চলেন নানান সামাজিক বার্তাসকল। সমসময়ের কাছে সাময়িক গুরুত্ব পাওয়া ছাড়া বৃহত্তর কাব্য-ইতিহাসে যাদের বিশেষ কোনও ভূমিকা নেই বলেই আমার মনে হয়। ‘মূর্খ বড়ো, সামাজিক নয়’ যিনি লেখেন তিনি যদি এমন সমাজসর্বস্ব হন, তাহলে তো লোকে ওঁর সম্পর্কে আলবাত বলবে-- সামাজিক বড়ো, মূর্খ নন মোটেই। হ্যাঁ, কবিতায় মূর্খের বিস্ময়, শিশুর বিস্ময় অবশ্যম্ভাবী শর্ত বৈ কী। একমাত্র ত্রিকালদর্শী স্থিতপ্রজ্ঞ লেখক ছাড়া, কাউকেই কবিতায় অত দায়িত্ববান দাদাবাবু হলে চলে না। দ্বিতীয়টি হলো— একজন মানুষ, যাঁর জীবনে অধ্যাত্মবাদের বিন্দুমাত্র জায়গা নেই, উপরন্তু, অধ্যাত্মবাদ প্রসঙ্গে যাঁকে নানারকম তুচ্ছতাচ্ছিল্য করতেও আমি প্রত্যক্ষ করেছি স্বয়ং, তিনি সারাজীবন ধরে রবীন্দ্রনাথকে ঠিক কী চোখে দেখলেন, সেটাই আমি ভেবে পাই না। অথবা রবীন্দ্রবিশেষজ্ঞই বা হয়ে উঠলেন কোন ম্যাজিক, কোন মন্ত্রবলে? কেননা রবীন্দ্রনাথের জীবনে প্রেম প্রকৃতি সমাজ, সবের ভেতর দিয়েই স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হচ্ছে অধ্যাত্মবাদ। অধ্যাত্মবাদের অর্থ যে পূজা-অর্চনা-ব্রত-রোজা-নমাজেই সীমাবদ্ধ তা তো নয়, ‘আকাশ ভরা সূর্য তারা’ গানটাতেও একটা গভীর আধ্যাত্মিক বিস্ময় আছে। এসব আড়াল করার চেষ্টা করে রবীন্দ্রনাথকে আদৌ বোঝা যায় কি? অথচ শঙ্খবাবু যেন সারাজীবন সেই ব্যর্থ চেষ্টাই চালিয়ে গেলেন। কিন্তু ওঁর ‘নিঃশব্দের তর্জনী’, ‘শব্দ আর সত্য’ ‘নির্মাণ আর সৃষ্টি’ জাতীয় প্রবন্ধের বই কিংবা ধরো, ‘সকালবেলার আলো’, ‘সুপুরিবনের সারি’ জাতীয় গদ্যরচনা আমার বিশেষ প্রিয়। এমনকী প্রাবন্ধিক হিসেবে ওঁর অভিভাবকত্বও আমার কাছে খুবই প্রার্থনীয়। ‘অন্ধের স্পর্শের মতো’ বইটি আমার সারাজীবনের পাঠক্রমে চির অমলিন হয়ে থাকবে, এ আমার স্থির বিশ্বাস।
কবীর সুমন আমার কাছে একটা ট্র্যাজেডি। আমি সুমনের আবির্ভাব থেকেই ওঁর গানের পরম ভক্ত। ওঁর লিরিক তুলনাহীন, ওঁর বিচিত্রগামী সুরের ধারণাও আমাকে বেশ অবাক করত। ওয়েস্টার্ন ক্লাসিক্যাল থেকে ভারতীয় মার্গ সঙ্গীত, সবরকম সুরেই ওঁর গানের গতিবিধি দেখে মুগ্ধ হতাম খুবই। কিন্তু লোকটা নিজের সীমা জানেন না। জানেন না, উনি ছাড়াও নানান মানুষ এখনও এই বাংলায় জীবিত আছেন যাঁরা নিয়মিত উঁচু দরের গানবাজনার খবর রাখেন। ওঁকে, শিল্পী হিসেবে আমি তবু হয়তো শ্রদ্ধা করতে পারতাম, যদি উনি এই বুড়োবয়সে বাংলা খেয়ালের নাম করে নিজের দুর্বিনীত অযোগ্যতার বদ-ঢেঁকুরটি না তুলতেন। উনি এত জানেন, আর এটা জানেন না যে ধ্রুপদী সংগীত মঞ্চে উঠে গাইতে গেলে গুরুকৃপা চাই, দীর্ঘদিনের সাধনামগ্ন তালিম চাই। ওঁর তো এসব কিছুই নেই। গলা থেকে সুরও বিদায় নিয়েছে বহু আগেই। তারপরেও যদি কোনও যশলোলুপ বামন চাঁদে হাত দিতে চায়, তার সম্পর্কে আর কীইবা বলার থাকতে পারে?
আর ব্যক্তিমানুষ হিসেবে কিংবা রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে সুমন সবদিক থেকেই অতি নিকৃষ্ট, অতি ধান্দাবাজ। তাই ব্যক্তি সুমন সম্পর্কে আমার কিছুই বলার ছিল না কোনও দিন, আজও নেই।
১০) তোমার এবং তোমার বন্ধুবৃত্তের কবিদের নিয়ে একধরণের কথা বাংলা কবিতা-বাজারে প্রচলিত।সেটা হল যে,তোমরা জীবনানন্দ, বিনয়ের অনুসারী এবং যখন তোমরা এক বিশ্বাস থেকে অন্য বিশ্বাসে যাও তখন একই সঙ্গে একই দিকে চলো। এই অভিযোগ সম্বন্ধে কি বলবে?
উত্তর— অভিযোগটি আংশিক সত্য বৈ কী। তবে সেই অংশটা এতই নগণ্য যে তা নিয়ে কখনও প্রশ্নের মুখে পড়তে হবে ভাবিনি। নয়ের দশকের শেষের দিকে জীবনানন্দের কাব্যে নানান আবিষ্কারের আলো এসে পড়ছিল, যার ফলে তখন জীবনানন্দের প্রাসঙ্গিকতা আমাদের কাছেও বিশেষ প্রাধান্য পাচ্ছিল। আমার ধারণা, তরুণ কবিদের ওপর অত বড় একজন কবির প্রভাব পড়াটাই সুস্থতার লক্ষণ। তাছাড়া আমরা দেখেছি গত শতাব্দীর পাঁচের দশকের অধিকাংশ প্রধান কবির লেখায় জীবনানন্দ অনুসারী হবার প্রবণতা স্পষ্ট। শক্তি বিনয় উৎপল এই তিন প্রধান কবিই ভাষাগত দিক থেকে এবং আংশিকভাবে ভাবের দিক থেকেও, স্পষ্টতই জীবনানন্দ অনুসারী। আগুন থেকেই তো আগুন জ্বলে। আর বিনয়ের কবিতা বিষয়ে আমাদের বিশেষ শ্রদ্ধা তখনও ছিল, এখনও আছে। এই পর্যন্ত অভিযোগকারীদের সঙ্গে আমি একমত।
অভিযোগটির নগণ্যতার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই এইবার। যারা অভিযোগটি করেন, তারা তাদের আংশিক অভিজ্ঞতার ঝুলিতে এই খবরগুলি সংগ্রহে রাখতে ভুলে গেছেন যে ‘গান্ধার’ পত্রিকা গোষ্ঠীর অধিকাংশ সদস্য শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতায়, উৎপলকুমার বসুর কবিতায় গভীর ভাবে আচ্ছন্ন থেকেছে দীর্ঘকাল। আরও একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিতে চাই এই প্রসঙ্গে। কফি হাউসের ওই আড্ডায় যোগ দেওয়ার পরেই আমি জানতে পারি যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও একজন বড় কবি, অবশ্যমান্য কবি। তার আগে পর্যন্ত তো আধুনিকতার ধ্বজাধারীরা আমাদের কানে অনবরত মন্ত্র দিয়ে চলতেন যে রবীন্দ্রনাথ অনাধুনিক, তার কাব্যে আধুনিক জীবনের ঘাত-প্রতিঘাত নেই, উনি বুর্জোয়া, জমিদার বাড়ির ছেলে, ক্ষুধার্ত সর্বহারা মানুষের জীবন থেকে তাঁর জীবন দর্শন অনেক দূরবর্তী... এইসব... সুতরাং গান্ধারের কবিগোষ্ঠী যে শুধু জীবনানন্দ দাশ বা বিনয় মজুমদারের অনুগামী ছিল তা একেবারেই নয়, তাদের চেতনায় বাংলা তথা বিশ্বসাহিত্যের বহু শ্রেষ্ঠ কবির প্রভাবই কাজ করেছে। কিন্তু সবকিছুর পরেও বলছি, কবিতা কোনও দলগত কাজ নয়। হয়তো সেকারণেই আমাদের গোষ্ঠীটিও অবলুপ্ত হয়েছে একদিন। না কোনও ঝঞ্ঝাট ঝামেলা নয়। অয়ন চক্রবর্তী ছিল তখন ওই আড্ডার প্রধান পৃষ্ঠপোষক। অয়ন ব্যস্ত হয়ে পড়ল সাংবাদিকতার কাজে। অন্যান্যরাও জীবিকার তাড়না অনুভব করল একে একে। ফলে সেই আড্ডা নিয়মিত ধরে রাখার মতো পরিস্থিতি আর রইল না। যদিও তার রেশ, একটা টেবিল ঘিরে এখনও আছে, কিন্তু তা আর আগের মতো কবিতাপ্রধান আড্ডা নয় মোটই।
দলের কথা তো গেল, এবার নিজের দু’একটা কথা বলি। আমি বাংলা কাব্যে চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি মধুসূদন রবীন্দ্রনাথ জীবনানন্দ সুধীন্দ্রনাথ শক্তি বিনয় যুগান্তর পার্থপ্রতিম প্রমুখ এবং বিশ্ব কবিতায় রুমি, জিব্রান, কিটস্, ব্লেক, ইয়েটস্, হুইটম্যান, পুশকিন, বোদলেয়ার, রিলকে, পাস্তেরনাক, ফ্রস্ট, হিমেনেথ প্রমুখ কবির কবিতার অনুসারী। আমার প্রভাবিত হওয়ার ধরনটি সর্বগ্রাসী। পৃথিবীর যে কোনও শ্রেষ্ঠ কবির দ্বারা, এমনকী অন্যান্য শিল্পমাধ্যমের শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার জন্য আমার মন সবসময়ই উদগ্রীব হয়ে থাকে।
প্রশ্ন ১১)কবিতা লিখে রাষ্ট্রের পুরস্কার বা পত্রিকা গোষ্ঠির পুরস্কার, এগুলো নিয়ে কী ভাবো?
উত্তর—পুরস্কার নিয়ে এখন আর কিছুই ভাবি না। আগে একসময় ভাবতাম, যখন মনে করতাম, কবিতায় পুরস্কার দেওয়া হয় ভালো লেখার জন্য। কিন্তু দীর্ঘদিন যাবত এইসব রাষ্টীয় এবং পত্রিকাগোষ্ঠীসমূহের দেওয়া পুরস্কারের সার্কাস দেখতে দেখতে আমার স্থির বিশ্বাস জন্মেছে যে ভালো লেখার জন্য কোনও পুরস্কারই দেওয়া হয় না আদৌ, তার পেছনে অন্য নানান সমীকরণ কাজ করে। রাজনৈতিক দল বা ক্ষমতাবান ব্যক্তির তাঁবেদারি না করে, আমাদের রাজ্যে বা দেশে, কেউ কোনও পুরস্কারই পায় বলে আমার মনে হয় না। কেউ কেউ যদি দৈবাৎ পেয়েও যায় বা যান, সেটা একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যতিক্রম বলে ধার্য হওয়া উচিত। সুতরাং কেউ পুরস্কার পেলেও পেল, না পেলে না পেল, নিলেও নিল, না নিলে না নিল, ব্যাপারটা এইরকম। কেননা পুরস্কার ব্যাপারটা এতোই বাহ্যিক যে সেটা নিয়ে না ভাবলেও কবিতা লেখার ক্ষেত্রে কোনও ক্ষতিবৃদ্ধি নেই।
প্রশ্ন ১২) তোমার নিজের লেখা সম্বন্ধে তোমার কী মনে হয়, মানে নিজের ক্ষমতা নিয়ে, সীমাবদ্ধতা নিয়ে কিছু ভেবেছ?
উত্তর—নিজের ক্ষমতা নিয়ে নিজে মুখে কিছু বলার ইচ্ছে আমার নেই। কারণ আমি আগেই বলেছি, কবিতা আমি লিখিনা, বরং কবিতাই আমাকে রচনা করে স্বয়ং। আমার কাজ আধার হিসেবে নিজেকে নিমগ্ন রাখা। সেটা হতে পারে প্রকৃতির নিবিড় সান্নিধ্যের মাধ্যমে, আগ্রাসী কবিতা পাঠের মাধ্যমে, অন্যান্য পড়াশুনোর মাধ্যমে, ছন্দ শিক্ষার মাধ্যমে, গান শোনার মাধ্যমে, ফুটপাথে ফুটপাথে অকারণ ঘুরে ফেরার মাধ্যমে, মানুষের সঙ্গে মেলামেশার মাধ্যমে, নিভৃত কোনও অবকাশে আত্ম-উপলব্ধির মাধ্যমে, আত্মবিলোপের মাধ্যমে। সেই প্রসঙ্গে আজ এটা নির্দ্বিধায় বলতে পারি, এখনও পর্যন্ত আমার কবিতাজীবনে সীমাবদ্ধতা বিপুল। জীবন যে অফুরন্ত ভাণ্ডার আমার সামনে মেলে ধরেছে এযাবৎকাল, তার খুব কম অংশই আমি সার্থক কবিতা হিসেবে ধরে রাখতে পেরেছি। আসলে কবিতার জন্য যে সমর্পণের জীবন দরকার, তা আমি গত কয়েকবছর সার্বিকভাবে যাপন করে উঠতে পারছি না। জীবিকার তাড়নাতেই জীবনের অনেকটা ফুরিয়ে যাচ্ছে। লিখেওছি সেই কথা। ‘স্বপ্নে আগুনের মন্ত্র দিয়েছিলে / জ্বালানি কুড়োতেই জীবন জেরবার’। ফলে আধার হিসেবে নিজেকে সবসময় টনটনে সজাগ রাখার অবকাশ না পাওয়া, আমার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় সীমাবদ্ধতা এখন। আগে বহুদিন সেই যাপন করতে পেরেছি, ভবিষ্যতেও পারব আশা রাখি। তখন এই বর্তমান সীমাবদ্ধতাও অনেকটা কাটিয়ে উঠতে পারব, আমার ধারণা। অন্তত কাটিয়ে ওঠার আপ্রাণ চেষ্টা তো করবই। দেখা যাক জীবন সেই সুযোগ আমাকে আদৌ দেয় কিনা, বা দিলেও, কবে দেয়।
মতামত ব্যক্তিগত